কাঞ্চন নদীর পুরোনো ব্রিজটার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাকিয়ে ছিলাম দূরে, যতদূর দেখা যায় ততদূরে কোথাও। আমার সামনে নদী খানিকটা বেঁকে গেছে, সেই বাঁকের কাছে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কিছু ঘরবাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছিল। দূর থেকে সবকিছু কী ঝকঝকে পরিষ্কার! আমি নিশ্চিত কাছে গেলে চোখে অন্য রকম হয়ে যাবে। কোনো বাড়ির ভাঙা একটা ঘর চোখে পড়বে, আশপাশে ময়লার স্তূপ দেখা যাবে। ঘরের ভেতরের ভাঙন অবশ্য সাদা চোখে দেখা যায় না। সেইসব গাদাগাদি ঘরের ভেতরে হাজার রকম প্রেম-অপ্রেমের গল্প দূরের ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে কল্পনা করতে ভালোই লাগছিল। যেন পাখির চোখ দিয়ে দেখছি। লেখকদের পাখির চোখ দিয়েই দেখতে হয়। তবে দূর থেকে দেখলেও তারা দেখে কাছের চেয়ে কাছে থেকে দেখার মতো করে।
উল্টো দিকে ফিরতেই আমার সামনে রেলের ব্রিজ। একটা ট্রেন দ্রুত চলে গিয়ে সেদিকে আমার মনোযোগ টেনে নিল। ট্রেনের ব্রিজের দুটো জায়গায় বাড়ানো বারান্দা। এখানকার স্থানীয় লোকেরা বলত পকেট। পকেটে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকজন মানুষ। নদীর ওপরের বাতাস কেটে ট্রেনটার চলে যাওয়ায় সেখানে যেন বাতাসের একটা ঘূর্ণি লেগে গেল। পকেটে দাঁড়ানো একটা মেয়ের লাল ওড়না আর সবুজ কামিজ উড়ছিল। ওড়া দেখে মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের পতাকা। ট্রেন চলে গেলে আবার চোখ গেল অবারিত সামনের দিকে। কিন্তু দৃষ্টি কেন যেন কিছুতেই আর প্রসারিত হচ্ছিল না। লালচে লোহার ব্রিজটার পিলারগুলোর নিচের দিকে চোখ আটকে যাচ্ছিল। কোনো এক সময়ে ওই পকেটে দাঁড়িয়ে আমি চুপচাপ নিচের ওই পিলারগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভরা বর্ষায় পাহাড়ি স্রোতে পিলারে বাধা পেয়ে দুই ভাগ হয়ে যেত। সেদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা যেত তখন। বিকেলের পড়ে যাওয়া রোদে ব্রিজের পকেটে দাঁড়িয়ে থাকার নেশা ছিল আমার। মাঝেমধ্যে ট্রেন এসে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে ওড়ার মতো অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন করে চলে যেত। কেন ওখানে বসে থাকতাম আমি? বিরল কলেজ থেকে ফেরার পথে নদী পার হবার কোনো রাস্তা ছিল না। রেল ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে পার হতে হতো। ওপারে গিয়ে আরেকটা রিকশা নিয়ে নিতাম। রেল ব্রিজে পা দেবার পরে যদি ট্রেন চলে আসত তখন পকেটে দাঁড়ানো ছাড়া গতি থাকত না। আর ঠিক তখনই আমার চোখ চলে যেত নিচের পিলারের পায়ের কাছে বাধা পাওয়া স্রোতের দিকে। কলেজের একজন অধ্যাপক বাড়ি যাবার তাড়া ভুলে ব্রিজের পকেটে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে কিংবা পা ঝুলিয়ে পকেটে বসে আছে, পরিচিত কারো দেখতে কেমন লাগত আমার জানা নেই। কখনো কোনো ছাত্র ওই অবস্থাতেই সালাম দিয়ে দ্রুত সরে যেত। এক মুহূর্তের জন্য লজ্জা পেয়েই আমি ঝোলানো পায়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে ধাক্কা খাওয়া সাদা ফেনার দিকে চোখ ফেরাতাম আবার। তারপর অন্ধকার নামতে থাকলে ধীরে ধীরে বাসার পথে এগোতাম। ওই বয়সে বাসায় স্ত্রী-কন্যা রেখে ব্রিজে বসে হাওয়া খাওয়া আর কতক্ষণ মানায়?
রেণু অবশ্য আমার ব্যাপারটা জানত। দুপুরে ক্লাস শেষ হলেও বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হলে একা হাতে সংসার সামলে রেণুর আমার ওপরে রাগ করার কথা ছিল। কিন্তু সে রাগ করত না। বরং খাবার টেবিলে দিয়ে মাঝেমধ্যে খানিক উৎসাহ দেখাত, ‘নতুন কোনো গল্পের প্লট পাওয়া গেল নাকি পানির স্রোত দেখতে দেখতে?’ আমি হাসতাম। স্রোত দেখে কি গল্পের প্লট পাওয়া যাবে? রেণু যে কী একটা! গল্প তো উঠে আসে জীবন থেকে, জীবনকে মন্থন করেই টুকরো টুকরো গল্প। কত দিন সকালে উঠে রেণুর ফোলা ফোলা মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মাথায় কত গল্পের প্লট এসেছে, সেসব রেণুকে বলা হয়নি। রেণু সব সময় ব্যস্ত সে দিনগুলোতে। তিন বছরের ছটফটে বাচ্চাটা সামলে সারা দিন একা হাতে সংসারের সব কাজ করা সোজা কথা নয়। তবে সে এই ভেবেই প্রশান্তিতে থাকত যে আমি গল্পের প্লট খুঁজে বেড়াই, তাই আমার বাড়ি ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। দেশের বড় বড় দৈনিকের কোনো না কোনোটাতে আমার গল্প ছাপা হতে থাকত তখন, ধীরে ধীরে নামডাক হচ্ছিল। আমার লেখকসত্তা নিয়ে রেণুর গর্বের শেষ ছিল না। আর গর্ব করতে দেখতাম আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েদের।
দেশের আলোচিত একজন তরুণ গল্পকার তাদের শিক্ষক, এ নিয়ে তাদের আনন্দ ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। তারা মনে করত গল্পে যেহেতু কাহিনির জটিলতার সমাধান করতে পারি, তাই পৃথিবীর যেকোনো সমস্যার সমাধান আমার কাছে আছে। ব্যক্তিগত হোক আর যা-ই হোক না কেন, সমস্যায় পড়লে আমার কাছে আসত। তখন আমি পড়তাম বিপদে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আমার সদ্য প্রকাশিত কোনো গল্প নিয়ে আলোচনার তুবড়ি ছুটত। কীভাবে লিখলাম, কী করে এরকম একটা কিছু মাথায় এল, তারা তাদের কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারত না। সেসব বহু আগের কথা; অন্তত বত্রিশ বছর। বিরলের সেই কলেজ নিশ্চয় তারপর অনেক বড় হয়েছে। তখনকার লম্বালম্বি টিনের ছাদওলা বিল্ডিংয়ের জায়গায় তিনতলা উঠেছে শুনেছি। ঢাকা থেকে দিনাজপুর যাবার সময়েই ভেবে গিয়েছিলাম, একবার দেখতে যাব। দিন তিনেক থাকব পর্যটনের হোটেলে, একবার তো যাওয়াই যায়। এই যেমন সেদিন দেখতে গেলাম কাঞ্চন নদী। দেখে অবশ্য মন খারাপই হলো বলা যায়। স্রোতে টইটুম্বর এ-পার, ও-পার ভরপুর নদী কেমন খাঁ খাঁ করছিল। যেখানে পানির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতাম, আচ্ছা, এখানে সব পানির ওজন ঠিক কত হতে পারে?সেখানে আজ সত্যিই এত কম পানি যে ওজন মাপা যাবে। মাঝে মাঝে সাদা আর বাদামি-রুপালি বালুর চর জেগে ছিল, তারই ফাঁক-ফোকর দিয়ে সরু নালামতো চলে গেছে কিছু। একা একা খানিক দূরে গিয়ে একটা নালা আরেকটার সঙ্গে মিলে গেছে, তারপর দুজনে মিলে আবার রওনা দিয়েছে এক হয়ে। সর্পিল এই ক্ষীণ নালাগুলোর ভিড়ে আমার চোখে লেগে থাকা তিরিশ বছর আগের কাঞ্চন নদীকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। যেন মনে হলো দুদিক থেকে পাড়ও এগিয়ে এসেছে। নদী দখলের অভিশাপ থেকে কি এই বিশাল অবাধ্য পুনর্ভবারও মুক্তি নেই? আমি পাড়ের বিস্তৃত খেতের দিকে তাকালাম। দেখলাম দূরে ইটের ভাটার চিমনিগুলো চিরুনির দাঁড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়গুলো থেকে সাদা ধোঁয়া ফাঁকা আকাশটাকে মেঘময় করে ফেলেছে যেন। একজন কেউ খুব কাছে এসে পড়েছে দেখে আকাশের কৃত্রিম মেঘ থেকে চোখ নামাতে হলো।
‘স্লামালিকুম, স্যার, কেমন আছেন?’
‘ভালো আছি। আপনি?’- দেখলাম পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়সি এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, পরনে সরু নীল পাড়ের হলদে শাড়ি। ও রকম শাড়ি মেয়েরা বসন্তের প্রথম দিনে পরে, আমি লক্ষ করেছি, যে রংটাকে তারা বলে বাসন্তী। তখন নভেস্বর মাস, মেয়েটা কেন ওরকম বাসন্তী সাজে সেজেছিল আমি বুঝিনি। আমি এ-ও বুঝিনি যে সে আমাকে চেনে কি না। তবে তার মুখের দিকে খনিক তাকিয়ে মনে হলো যেন কোথাও দেখেছি।
‘আমাকে চিনতে পারলেন না তো?’
‘না, ঠিক মনে পড়ছে না, তবে কোথাও যেন-’
‘দেখেছেন, তাই না? আচ্ছা, সত্যিই কি মনে নেই আমাকে?’
আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তার কথা বলার ভঙ্গিতে অবশ্য এমন কিছু একটা ছিল যেন সে আমাকে অনেক দিন থেকে জানে। তার সেই আন্তরিক ভঙ্গির জন্যই হয়তো নিশ্চিত হলাম যে তাকে চিনতাম,কোথাও দেখা হয়েছে। রিটায়ারমেন্টের আগে তিতুমীর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম, সেখানকার কোনো ছাত্রী হতে পারে কি? ভাবলাম, থাক অত ভেবে লাভ কী, জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়।
‘আমি সত্যিই মনে করতে পারছি না। বয়স হয়েছে তো, আগে দেখেছি আপনাকে?’
‘ছয় বছর আগে আপনি আমাকে তুমি বলতেন।’
‘আচ্ছা। কী নাম তোমার?’
‘আমার নাম জিনিয়া। আমার মায়ের নাম জবা। এবারে মনে পড়েছে, স্যার?’
নাম শুনেই আমি বোকা বোকা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চেহারা ভুলে গেছি কিন্তু এই নাম আমি কেমন করে ভুলি? বাড়িতে রেণু উঠতে-বসতে কতবার এই নাম দুটো নিয়ে আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মেরেছে। আবার এই নামের কারণে রেণুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাও যে দেখিনি, তা নয়। আমি সামান্য হেসে মেয়েটির দিকে তাকালাম।
‘চিনতে পেরেছি। কেমন আছ জিনিয়া? বিরলেই থাক এখনো?’
‘না, আমি দিনাজপুর শহরে। সরকারি গার্লস স্কুলে পড়াই।’
‘বাহ্ খুব ভালো।’
‘ওই যে গণেশতলায় স্কুল আর আমি থাকি মুন্সিপাড়ায়। সোজা মেইন রোড ধরে যেতে হয়। এখন কিন্তু দিনাজপুর শহর আর তত নিরিবিলি নেই। একটু পরপরই গাড়ি চলছে, আর গাড়ি একবার চাপা দিলে-’
‘বলো কী! কাকে চাপা দিল?’
জিনিয়া চমকে উঠল। পরমুহূর্তে মনে হলো কিছু যেন লুকাতে চাইছে। খানিকটা বিব্রত দেখাল তাকে। এই কয় বছরের মধ্যে ছিমছাম দিনাজপুর শহরের রাস্তা এত খারাপ হয়ে গেল নাকি? কথায় কথায় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে? তবে আমি আর কথা বাড়ালাম না রাস্তাঘাটের অবস্থা নিয়ে, বললাম, ‘কবে থেকে স্কুলে পড়াচ্ছ?’
‘এই তো প্রায় ছয় বছর। সেই যে আপনার সঙ্গে ঢাকায় দেখা হলো, তারপর ফিরে এসেই জয়েন করেছি। টানা ছয় বছর ক্লাস এইটে পড়ালাম। অনেক দিন, না?’
‘অনেক দিন বটে। তবে ছয় কেন শুধু, আরো অনেক বছর পড়াও।’
জিনিয়া আবার চমকে উঠল। মনে হলো কিছু অন্যায় বলেছি। আমি তার বিস্ময় দেখেও দেখলাম না। কে জানে চাকরি নিয়ে কোনো জটিলতা হয়েছে কি না, হয়তো আমাকে বলতে চায় না। বিস্ময় কেটে গিয়ে জিনিয়ার মুখ কেমন যেন মায়াময় হয়ে গেল। মনে হলো এক্ষুনই কেঁদে ফেলবে। কান্না লুকাতেই হয়তো সে রেল ব্রিজের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। তার বাসন্তী আর নীলে মাখামাখি শাড়ির আঁচল বাতাসে পেছন দিকে উড়ে চলে যেতে চাইল যেন। ব্রিজের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে মুচকি হেসে জিনিয়া বলল, ‘মনে আছে, আপনার বাড়িতে গিয়ে কী সব কাণ্ড করলাম আমি?’
আমি হাসলাম। মনে ছিল সবই। শুধু জিনিয়ার মুখটাই কেন যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছিল। কিংবা সে সালোয়ার কামিজ পরে আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তাই সেদিন শাড়িতে অন্য রকম লেগেছে বলে চিনতে পারিনি। তখন সব মনে পড়লেও জিনিয়াকে সেসব বলে বিব্রত করতে চাইনি। কিন্তু তাকে না বললেও, আমার মাথায় একের পর এক সেদিনের ঘটনাগুলো আনাগোনা করছিল।
হালকা শীতের সকাল ছিল। রিটায়ারমেন্টের পর থেকে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার বদভ্যাস হয়েছিল আমার। রাত জেগে লিখতাম। সেদিন সকালেও বেশ দেরি করে উঠে বাইরের বারান্দায় রোদে বসে পেপার পড়ছিলাম। দেখলাম বাড়ির গেট খুলে একটা মেয়ে গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকে গেটটা ভিড়িয়ে সে বাসার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিল। ভাবলাম ওপরের কোনো তলায় যাবে হয়তো। কিন্তু সে সোজা আমাদের দরজার দিকে এগিয়ে এল। বাসাটা নিচতলায়, তাই বাগানের দিক থেকে একটা গ্রিলের দরজা ছিল। মেয়েটা আমাকে লক্ষ করে সোজা সেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় হাত রেখে বলল, ‘লেখক রাজীব আহমেদ, আমার আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।’
‘কী ব্যাপার বলুন তো?’- পেপার বন্ধ করে চমকে উঠলাম আমি। এভাবে বাড়ি বয়ে এসে এত দৃঢ় কণ্ঠস্বর কেউ আমাকে শোনায়নি কখনো।
‘দরজা তো খুলুন আগে, তারপর বলি।’-একই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলল সে। অচেনা একটা মেয়েকে দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকতে দেব কি না, এ নিয়ে আমি কয়েক সেকেন্ডের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেলাম। মেয়েটা আমার অবস্থা দেখে বলল, ‘আপনার অশরীরী গল্পটার কথা মনে নেই? এমনই তো একজন এসেছিল লেখকের বাড়িতে। লেখক তো ঠিকই তাকে দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। লেখার সময়ে লিখে ফেলেছেন, অথচ দেখুন বাস্তবে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন বাইরেই।’
আমি দরজা খুলে দিলাম। সে এমনভাবে আমার পাশের চেয়ার টেনে বসল যেন এ বাড়িতে সে বহুবার এসেছে। আমি চুপচাপ তার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কোথাও না কোথাও যেন অদ্ভুত একটা চেনা চেনা ব্যাপার কাজ করছিল তার কথার ভঙ্গিতে।
‘আপনারা লেখকেরা কিন্তু লেখার সময়ে যা খুশি তাই লেখেন, চরিত্ররা আপনাদের মনমতো চলবে-ফিরবে, কথা বলবে, কিন্তু বাস্তবে সেটা হলে আপনারা দারুণ ঝামেলায় পড়ে যাবেন, সেটা জানেন?’
আমি হাসলাম। পাঠকদের নানান পাগলামো প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ভাবলাম কোনো গল্প পড়ে উত্তেজিত হয়েই তার আগমন। মনে মনে তার বলা অশরীরী গল্পের কথা মনে করার চেষ্টা করলাম। মনে পড়ল না। বহু বছর আগের লেখা হয়তো। মেয়েটি বয়সে আমার মেয়ের চেয়েও ছোট হবে, তাই ভাবলাম ‘তুমি’ বলতে দোষ নেই।
‘তোমার নাম কী? কোথা থেকে আসছ বলো তো?’
‘আমার নাম জিনিয়া। আসছি দিনাজপুরের বিরল থেকে।’
‘তাই নাকি! আমি তো ওখানকার কলেজে বছর তিনেক পড়িয়েছিলাম। জায়গাটা চিনি।’
‘সেটা জেনেই এসেছি আমি। বলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই আমি আপনার সেখানে থাকার কথা জানি।’
‘আচ্ছা! কীভাবে? তুমি তো আর আমার ছাত্রী হতে পারো না।’
‘আমি নই, আমার মা আপনার ছাত্রী ছিলেন। ওনার নাম ছিল জবা।’
‘ছিল মানে? জবা কি নেই?’
প্রশ্নটা করতে গিয়ে অনেক কিছুই একসঙ্গে মনে পড়ছিল। জবা কোনো নোটিশ ছাড়াই কোনোদিন বঙ্কিম, কোনোদিন রবীন্দ্রনাথ বুঝতে আমার রুমে আসত। বেশির ভাগ আসত খাঁ খাঁ দুপুরে, যখন করিডর পর্যন্ত সুনসান হয়ে যেত। আমার অস্বস্তি হলেও মনোযোগ দিয়ে তাকে বোঝাতাম। সিলেবাসের বাইরেও কোনোদিন কমল মজুমদারের কোনো উপন্যাসের একটা পাতা খুলে নিয়ে হাজির হতো। বিরলের মতো ছোট একটা উপজেলা শহরে সে ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সাহিত্য পড়ার ওরকম তাড়না দেখিনি। তাই আমিও ছাত্রী হিসেবে তাকে পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কদিনেই বুঝতে বাকি থাকল না যে জবা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিও দুর্বল। দেখলাম, যা পড়তে আসে তা পড়া শেষ করেও আধা ঘণ্টা ধরে আমার কোনো গল্প নিয়ে কথা চালিয়ে যায়। প্রথম প্রথম ভক্ত পাঠক হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝলাম তার ভাবভঙ্গি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। ছিপছিপে তরুণী জবা, কথার ফাঁকে তার কোমর ছাপিয়ে নামা অবাধ্য চুলগুলোকে প্রায়ই হাত দিয়ে পেঁচিয়ে খোঁপা করে রাখত, কিছুক্ষণ পরে ঝুপ করে খোঁপা খুলে ঝরঝরে চুল তার চোখ ঢেকে দিত। জবা দ্রুত চুলগুলোকে কানের পেছনে পাঠিয়ে বইয়ের অক্ষরে কিংবা আমার কথায় ডুবে যেত। আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুগ্ধ চোখ ঘোলা হয়ে আসত। আমার তখন বয়সই বা কী, শ্যামলামতো মায়া করা মেয়েটা দু-এক দিন বাদে এসে মায়া করে তাকিয়ে থাকবে আর আমার মনে কোনো আবেগই আসবে না, তা কী করে সম্ভব! আমি ভেতরে ভেতরে নিজের গলে যাওয়া টের পাচ্ছিলাম। কদিন সেটা ভেবে আমার ভালোও লাগছিল। যেন সারা শরীর-মনে অদ্ভুত এক পুলক জানান দিচ্ছিল। তখন আমিও জবাকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করলাম। সে আগে টেবিলে উল্টো দিকের চেয়ারে বসত, আমার আহ্বান বুঝেই হয়তো পাশের চেয়ারে এসে বসা শুরু করল। তার সঙ্গে ঠিক সহজ হতে পারতাম না আবার তাকে যে আসতে মানা করব সে ক্ষমতাও ছিল না। জবার সঙ্গে আমার তেমন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি আর কোথাও কোনো কথা চালাচালিও হয়নি অথচ বাড়িতে রেণু যেন কী করে আমার পরিবর্তনটা ঠিকই ধরে ফেলল। একদিন মন খারাপ করে বলল আমার আচরণ নাকি ভীষণভাবে বদলে যাচ্ছে। সেটুকু পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু তারপর বাচ্চা মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে বলল, সে নাকি একা, আমি নাকি তার সঙ্গে নেই আর ওই বাড়িতেও নাকি তার কিছুই নেই। এই কথা শোনার পরে রেণুর টলটলে চোখের দিকে তাকিয়ে আমার যেন নিজের প্রতি কেমন একটা ঘৃণা জন্মাল। রেণু বলছিল লেখকদের দু-চারজন প্রেমিকা থাকা নাকি স্বাভাবিক আর কলেজের অধ্যাপক হলে তো কথাই নেই, কলেজে সুন্দরী অল্পবয়সি ছাত্রীরা আছে। বলতে গিয়ে শেষের দিকে তার গলা ধরে এল। রেণুর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তীব্র অনুশোচনায় ডুবতে লাগলাম। গল্পে যাই লিখি, বাস্তবে রেণু আমার বউ, চোখের সামনে তাকে কষ্ট পেতে দেখতে পারি না। দুদিন পরে জবাকে বলে দিলাম যা বোঝার ক্লাসেই বুঝতে হবে, আমার রুমে মধ্য দুপুরের এই নিরিবিলি ক্লাস চলবে না। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে আমি তাকে আসতে মানা করলাম। জবা রুমে আর এল না। এমনকি তারপর থেকে জবা আর আমার চোখের দিকে তাকিয়েও কথা বলেনি। মূর্তির মতো ক্লাসে বসে থাকত আর যন্ত্রচালিতের মতো আসত-যেত।
‘কী ভাবছেন, স্যার? মনে পড়েছে ভালোমতো? মা মারা গেছেন বছর তিনেক হলো’, ভাবনার মাঝখানে জিনিয়ার গলা শুনলাম।
‘সে কী, এত অল্প বয়সে-’
‘জি, একেবারে হঠাৎ করে। সে যাই হোক, আপনার কথা তিনি বরাবর বলতেন। আপনার সমস্ত বইয়ের জন্য আমাদের বাড়িতে একটা আলাদা ছোটমতো শেলফ আছে। প্রকাশের দিন-তারিখ হিসেবে মা বইগুলো লাইন করে রাখতেন। সেভাবেই আছে এখনো। বেঁচে থাকতে আমাকে বারবার করে পড়তে বলতেন। ওসব গল্প-টল্প পড়ার ব্যাপারে আমি ছিলাম না। ক্লাসের পড়া পড়েই কূল পেতাম না তাই মায়ের কথা কখনো শুনিনি। কিন্তু মা মারা যাবার পরে হলো কী-’
জিনিয়া অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মায়ের মারা যাবার কষ্টটা হুট করে চাড়া দিয়ে উঠল কি? সেই ভেবে আমিও চুপ করে থাকলাম।
‘হলো কী, মায়ের আলমারিতে ওপরের তাকের পেছনের দিকে আমি শ` তিনেক চিঠির এক পোঁটলা খুঁজে পেলাম। সমস্ত আপনাকে লেখা।’
‘বলো কী!’
‘জি। মা আপনাকে যখন যা বলতে চাইতেন, চিঠিতে লিখে ফেলতেন। আমার কাছে এখানে কয়েকটা আছে। আপনাকে দেখাবার জন্য এনেছি, দেখবেন?’
আমার উত্তরের আশায় না থেকে জিনিয়া তার ব্যাগ থেকে দুটো খাম বের করল। বহুদিন পরে খামে পোরা ভাঁজ করা কাগজের চিঠি দেখলাম। একটা জিনিয়া নিজেই ভাঁজ খুলে আমার সামনে মেলে ধরল।
. . . আমি আমার মাথার ভেতরে সারাদিন আপনার সঙ্গে কথা বলি। স্যার, আপনি কেন আমাকে আপনার রুমে যেতে মানা করলেন? কেন? কেন? আপনার সঙ্গে কথা বলা হয় না বলে আমাকে প্রতিদিন চিঠি লিখতে হচ্ছে। চিঠিগুলো খামে ভরে আমি বাড়ি থেকে বেরও হই কিন্তু পোস্ট না করে ফিরে আসি। তারপর একখানে রেখে ধরে নেই পোস্ট করা হয়ে গেছে। তারপর থেকে আপনার উত্তরের আশায় দিনের পর দিন কাটতে থাকে। এই প্রত্যাশাটুকু ছাড়া আমি বাঁচতে পারতাম না। কিন্তু আপনার উত্তর আসে না। তাই একসময় আমি নিজেই উত্তর সাজিয়ে নেই। আপনার হাতের লেখায় সেসব দেখা যায়, আপনার কণ্ঠস্বরে সেসব শোনা যায়। . . .
লম্বা চিঠি পড়তে পড়তে আমি ভাবছিলাম মেয়েটা কি শেষ পর্যন্ত সিজোফ্রেনিক হয়ে গিয়েছিল নাকি?কিন্তু আমারই বা কী করার ছিল। আর মোটের ওপরে কথা হলো এই যে আমি তো তার এসব ব্যাপার জানতামও না। তার চেয়ে জবার মেয়ের এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী সেটা নিয়েই বরং ভাবা যেতে পারে। জিনিয়া চিঠির পর চিঠি ব্যাগ থেকে বের করতে থাকল। কোনো কোনো চিঠি আমার কোনো গল্প পাঠের রিভিউয়ের মতো। সেগুলো পেলে পত্রিকাওলারা ছাপিয়ে দেবে নিঃসন্দেহে; তবে অভিযোগগুলো বাদ দিয়ে, যেমন. . .
স্যার, আপনার প্রতি আমার দুর্বলতা অন্যায় হয়েছে, মানলাম, কিন্তু আপনার দুই দুয়ার গল্পের কথা ভাবুন; লোকটার বাড়িতে সংসার, অফিসে প্রেমিকা, কি রকম শান্তির একটা জীবন দেখিয়েছেন বলুন তো? সেটা কি অন্যায়? গল্পে লোকটা সংসারের প্রতিও কত দায়িত্ববান আবার প্রেমিকার জন্যও জান কোরবান করে দিচ্ছে। কোথাও তো আমি কোনো সমস্যা দেখিনি। আপনিও দেখাননি। কেউ কারো কথা জানল না, অসুবিধা কোথায় ছিল? আর আপনার পুরাতন প্রেম গল্পের কথা মনে আছে? লোকটার তিনটা প্রেমিকা ছিল। পরকীয়া বলে দুনিয়ায় কিছু আছে বলেই সে বিশ্বাস করে না। তার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার যে মানুষ বহুগামী আর সব প্রেমই তার মতে প্রথম প্রেম। কী অনায়াসেই না বিশ্বাস হয়ে যায় এসব কথা আপনার গল্পটা পড়লে! মানে, এই যেমন আপনার সঙ্গে আমার আগে প্রেম হয়নি, তো, হলে কি প্রথম প্রেমই হতো না? লেখার সময়ে যুক্তি দিয়ে লিখে ফেলেন আর বাস্তবে আমাকে এক কথায় ফেলে দিলেন?. . .
চিঠিগুলোতে হয় গদগদ প্রেম নয়তো অভিযোগের পর অভিযোগ। বুঝলাম না জিনিয়া এসব নিয়ে আমার কাছে কেন এসেছে। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তার মায়ের কষ্ট বা মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করবে না তো?আমার কিছুটা অস্বস্তি লাগতে লাগল। তবু চুপচাপ জিনিয়ার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করলাম। যা এনেছে, মোটামুটি সব চিঠি দেখা শেষ হলে জিনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। সেই অবসরে আমি রেণুকে জোরে করে ডেকে চা দিতে বলে দিলাম। রেণু হয়তো ভেতর থেকেই বুঝেছিল আমার কাছে কেউ এসেছে। কিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিল কিংবা রেণুর এমনিতে কৌতূহল কম তাই বারান্দায় আসেনি।
‘মা আমাকে অনেকবার বলেছিলেন আপনার লেখা পড়তে। শুধু আপনার কেন, অনেকেরই। আমি পড়িনি। কিন্তু তিন বছর আগে মা মারা যাবার পর থেকে আমি প্রচ-ভাবে মায়ের অভাব বোধ করতে লাগলাম। তখন মায়ের অবর্তমানে তার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করাই হয়ে দাঁড়াল বাড়িতে আমার একমাত্র কাজ। ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই চিঠির স্তূপ আবিষ্কার করলাম। একের পর এক রাত কাটতে লাগল আপনার জন্য মায়ের আবেগ-অনুভূতির কথা পড়ে পড়ে। মাস ছয়েক পরে মনে হলো, চিঠিগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এবারে চিঠির মানুষটিকে জানা দরকার। তাই আমি আপনার বইগুলো পড়া শুরু করলাম। দিনরাত ধরে সেসবও কয়েকবার করে পড়া হয়ে গেল। আশ্চর্য লাগল, আমরা জীবনের একটার পর একটা দিন পার করে করে যা শিখছি, যা কিছুর সম্মুখীন হচ্ছি, আপনি আগেই কী করে গল্পের পর গল্পে সেসব লিখে রেখেছেন? আমি সত্যিই আপনার ভক্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু তারপর থেকে আমার ঘুম হতো না, কেবল মনে হতো মায়ের অতৃপ্তিটা আমাকে মেটাতে হবে। এখনো তাই মনে হয়, মা আমার মনে আর শরীরে বাসা বেঁধেছেন। মা আমাকে বলে দেন কী করতে হবে।’
জিনিয়ার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম তা নয়, জবা তো ঠিকই ছিল, সিজোফ্রেনিক যদি কেউ হয়ে থাকে তো সে হলো জিনিয়া। এরপর কী শুনব ভাবতে পারছিলাম না।
‘তো, একদিন মনে হলো মা আমাকে ভেতর থেকে বলছেন যে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, আপনার কাছে আসতে হবে।’
‘তারপর?’
‘তারপর আর কী, চলে এলাম।’
‘শুধু আমাকে দেখার জন্য চলে এলে?’
জিনিয়া বড় নিঃশ্বাস নিল। মনে হলো যা বলতে চায় তার জন্য একটু প্রস্তুতি দরকার। সোজা হয়ে বসল। দেখতে খুব দৃঢ় দেখাল তখন তাকে।
‘না। আমি আসলে চাই আপনি আমাকে-’
জিনিয়ার কথা শেষ হতে পারল না, তার আগেই চা-নাশতার ট্রে হাতে রেণু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রেণুর চোখে প্রশ্ন ছিল। জিনিয়া উঠে সালাম দিয়ে ট্রে হাতে নিল। আমি রেণুর সঙ্গে জিনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলাম। ট্রে টেবিলে রেখে জিনিয়াই আমাদের হাতে চায়ের কাপ উঠিয়ে দিল।
‘তা, জিনিয়া, তুমি যেন কী চাও বলছিলে?’
জিনিয়া থতমত খেয়ে বলল, ‘আচ্ছা, পরে না-হয় বলব আপনাকে।’
‘পরে কেন? যে দরকারে তুমি এতদূর থেকে আমার কাছে এসেছ তা শুনব না?’
‘জি, অবশ্যই শুনবেন।’
‘বলো তাহলে।’
‘জি, আমি কি ওনার সামনেই বলব?’ রেণুর দিকে ইশারা করল জিনিয়া।
আমি নির্দ্বিধায় বললাম, ‘নিশ্চয়।’
‘মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি চাই আপনি আমাকে. . .আপনি আমাকে বিয়ে করেন।’
আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। আমার আঠাশ বছর বয়সি মেয়ে সামনে থাকলে হয়তো অবাক হয়ে জিনিয়ার দিকে তাকাত কিংবা রেগেও যেতে পারত। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমার জীবনে বয়সি বটের মতো দাঁড়িয়ে থাকা রেণু ফিক করে হেসে দিল। সেই হাসি দেখে জিনিয়া যারপরনাই বিব্রত হয়ে গেল। কথাটা সে ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছে বটে তবে রেণুর হাসিতে যেন কথাটার গভীরতা ধরতে পারল। রেণু চায়ের কাপ মুখের কাছে নিয়ে হাসি ঠেকাতে চেষ্টা করল।
‘দেখো, জিনিয়া, আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার প্রতি তোমার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এটা থেকে তুমি বেরোতে পারছ না, যে কারণে এতদূর ছুটে এসেছ। তুমি এক কাজ করো, আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থেকে যাও। আমরা তোমার সঙ্গে গল্প-টল্প করি, আমাদের বাস্তব জীবনটা তোমার বোঝা হয়ে গেলে আকর্ষণের মাত্রাটা বদলে যাবে, কেমন? আর হ্যাঁ, ঢাকায় উঠেছ কোথায়?’ বলেই জিনিয়ার চেয়ারের পাশে ভারী ব্যাগটা লক্ষ করলাম। আমার ধারণা ঠিকই ছিল, সে ঢাকায় পৌঁছে সরাসরি আমার বাসাতেই এসেছে।
‘আমি এখানে কোথাও ওঠার জন্য আসিনি। আপনাকে যেটা বলেছি তা আপনি করবেন কি না সেটা বলেন`, জেদি গলা শুনলাম জিনিয়ার।
‘বললে কি তুমি শুনবে?’
‘তার মানে আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন না, তাই তো?’
‘কী করে করি বলো তো-’
‘সমস্যা কোথায়? আমার বয়স পঁচিশ। বিয়ের জন্য ঠিক আছে না? দিনাজপুর সরকারি কলেজ থেকে এমএ পাস করেছি। সেখানে সবাই তো আমাকে সুন্দরীই বলত। একটা অবশ্য ভুল হয়েছে, আজ পয়লা ফাল্গুন, আমার সালোয়ার-কামিজ না পরে বাসন্তী শাড়ি পরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সে যাই হোক, সবার আমাকে ভালো লাগে, শুধু আপনার কেন আমাকে ভালো লাগবে না?’
রেণু মুখে চায়ের কাপ ঠেকিয়ে একবার আমার আরেকবার জিনিয়ার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। যখন যার কথা বলার কথা, তার দিকে। রেণুকে দেখে মনে হচ্ছিল কোর্টের মাঝামাঝি বসে ব্যাটমিন্টন খেলা দেখছে। জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সুন্দরীই বটে। তার মায়ের মতোই চুল পেয়েছে, গায়ের রং মায়ের চেয়ে আরেকটু উজ্জ্বল। বড় বড় পাপড়িওলা চোখে যেন রাজ্যের মায়া। সেই মুহূর্তে চোখজোড়া স্থির আমার দিকে, উত্তরের অপেক্ষায়। এতটুকু ভনিতা নেই সে চোখে।
‘দেখো, জিনিয়া, তুমি সব দিক দিয়ে ভালো। একটু বেশিই ভালো। যে কেউ তোমাকে বিয়ে করতে পারলে আনন্দিত হবে।’
‘যে কেউ না, আমি আপনার কথা জানতে চাচ্ছিলাম।’
‘সেটাই। আমার বয়স তেষট্টি। আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে কয়েক বছর আগে। সে তোমার চেয়েও বড়। তুমি এই অল্প বয়সে আমার মতো একটা বুড়ো লোককে বিয়ে করে কী করবে বলো তো?’
‘সেটা আমি বুঝব। আপনি শুধু রাজি আছেন কি না বলেন।’
জিনিয়া ভীষণ উত্তেজিত। বুঝলাম, বিপরীতে আমাকে ঠান্ডা হতে হবে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুরু করলাম।
‘আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে বিয়ে করতে হলে আমার স্ত্রী, রেণু আর আমার মেয়ের অনুমতি লাগবে? ওরা যে আমার পরিবারের সদস্য, বুঝতে পারছ?’
এবারে রেণু আর থাকতে পারল না। মুখ থেকে চায়ের কাপ সরিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। পরমুহূর্তে জিনিয়ার লাল হয়ে যাওয়া মুখ আর থরথর করে কাঁপতে থাকা ঠোঁট দেখে মনে হয় সংযত হলো। হাতে শাড়ির আঁচল নিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরল।
‘জিনিয়া, তোমার কি মনে হয় যে ওরা মত দেবে?’ আরো নরম গলায় জানতে চাইলাম আমি।
‘দেখুন, আমি আপনার মতটা জানতে চাচ্ছিলাম।’ কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে কোনো রকমে বলল জিনিয়া।
‘শোনো, আমার আবার মত কী, মানুষ যেমন বলে, মেয়েটার বিয়ের বয়স চলে গেল, সেরকম আমি মনে করি আমারও বিয়ের বয়স চলে গেছে, বুঝেছ? তুমি আরো আগে আসোনি কেন? . . .হা হা হা. . .’
রেণুর সাথে সাথে আমাকেও হাসতে দেখে জিনিয়ার কিছু একটা হলো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।
‘আমার আবেগের কোনো মূল্য যে আপনার কাছে নেই, সেটা আমি জানি। মনে রাখবেন, আমার মাকে আপনি এক কথায় মানা করে দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে ফেরানো অত সহজ হবে না।’
আমি কিছু বলার আগে রেণু চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। জিনিয়ার ঘাড়ে হাত রেখে শান্ত গলায় বলল, ‘দেখো মেয়ে, এভাবে তো হয় না, উনি যেটা বলেছেন সেটা শোনো। ঢাকায় কোথাও তো ওঠোনি মনে হচ্ছে, আমাদের এখানে দুটো দিন থাকো। ওনাকে কাছে থেকে দেখো, জানো, তারপর না-হয় ভাববে, কেমন?’
রেণুর কথায় জিনিয়া শান্ত হলো। আমার মেয়ের ঘরে ঠাঁই হলো তার। রেণুই সব ব্যবস্থা করে গুছিয়ে দিল। তারপর সত্যি দুই দিন জিনিয়া আমাদের বাড়িতে থেকে গেল। আমার সঙ্গে নয়, রেণুর সঙ্গেই বেশি সময় কাটত তার। গভীর রাত পর্যন্ত আমি আমার মেয়ের ঘর থেকে তাদের দুজনের হাসি-তামাশার শব্দ পেতাম। মেয়ে বিয়ে করে চলে যাবার পর থেকে রেণুকে এত জোরে হাসতে শুনিনি। জিনিয়া থাকাতে তাকে বেশ ফুরফুরে লাগছিল বহুদিন পর। আমি নিজের ঘরে ফেব্রুয়ারি বইমেলায় শেষ সপ্তাহে বেরোবে বলে একটা বইয়ের পাণ্ডলিপি নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। জিনিয়া রেণুর তদারকিতে খুব ভালো করে বুঝে নিল যে আমি আসলে ওই বাড়িতে মানুষ নই, বরং একটা ফার্নিচার। তবে আমাকে ফেলে রাখলেও চলে না, সময়মতো ব্লাড প্রেশারের ওষুধ, ইনসুলিন থেকে শুরু করে খাবার-দাবার সব পৌঁছে দিয়ে খাওয়া নিশ্চিত করতে হয়। সারা দিনে আমি চারটা কথাও নিজে থেকে বলি না। আমার কোনো সামাজিক জীবন নেই। কেউ আমার কাছে আসে না আর আমিও কারো কাছে যাই না। এসব দেখেশুনে অথবা হয়তো রেণুর কোনো জাদুতেই জিনিয়াকে মানানো গেল। তিন দিনের দিন যখন সে আমাদের বাসা ছাড়ছিল, রেণুর পা ছুঁয়ে সালাম করল। আমার দিকে একরাশ লজ্জা নিয়ে তাকাল। তারপর থেকে আর কখনো তার সঙ্গে দেখা বা যোগাযোগ হয়নি।
কাঞ্চন নদীর ব্রিজের চারদিকে আলো কমে এল। সাদা বালুগুলো কালচে হয়ে উঠল। জিনিয়ার শাড়ির বাসন্তী রংটাও সাদাটে মনে হচ্ছিল। শুধু আকাশে ছিল অসংখ্য রং, একটার ওপরে আরেকটা লেপে দেয়া অথচ স্পষ্টভাবে আলাদাও করা যায়। সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি।
‘স্যার, আমাকে ক্ষমা করেছেন?’
‘কিসের জন্য বলো তো?’
‘ওই যে, আমি কী সব বেয়াদবি করলাম আপনার বাড়ি গিয়ে। ভাবলে এখনো আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যার। তখন উত্তেজনার বশে চলে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে অনুশোচনায় আর ক্ষমা চাইতে যেতে পারিনি। আর হ্যাঁ, ম্যাডামকেও বলবেন তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তার মতো ভালো মানুষ আমি পৃথিবীতে খুব কম দেখেছি।’
‘সেসব আমরা কবেই ভুলে গেছি, জিনিয়া। বরং তোমাকে নিয়ে কত গল্প হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, রেণু আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা নিয়ে অনেক হাসাহাসিও হয়েছে’, বলতে গিয়ে হাসি ঠেকাতে পারলাম না। জিনিয়া লজ্জা পেল তারপর আমার হাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসতেও শুরু করল। প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, ‘এত দিন পরে দিনাজপুরে কেন এলেন, স্যার?’
‘একটা উপন্যাস লেখার কাজে। কয়েক বছর আগে দশ মাইলে ইয়াসমীন নামে একটা মেয়ে ধর্ষিত হয়ে পুলিশ কাস্টডিতে মারা গেল, মনে আছে? সেই বিষয়ে একটা উপন্যাস লিখব। তো ভাবলাম, এত দিন আগের স্মৃতি থেকে জায়গাগুলোর ব্যাপারে লেখা কি ঠিক হবে? তাই দিন তিনেকের জন্য এসেছি। সুইহারিতে পর্যটনের হোটেলে উঠলাম। সকালে দশ মাইলের আশপাশের এলাকা ঘুরে এসেছি। এখন হাতে সময় ছিল বলে একা একা পুরোনো রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’
‘রাত হয়ে গেল প্রায়। হোটেলে যাবেন না?’
‘হ্যাঁ, যাই। তুমিও তো শহরে যাবে, না?’
‘ঠিক জানি না কোন দিকে যাব।’
ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে জিনিয়া একবার দিনাজপুর শহর আরেকবার উল্টো দিকে বিরলের দিকে তাকাল। তাকে কেমন যেন বিভ্রান্ত আর একই সঙ্গে ভীষণ অসহায় মনে হলো। আমি তাকে খুশি করার জন্য বললাম, ‘বাড়ি যাও। আরো দুদিন আছি তো, ঘুরতে ঘুরতে তোমার স্কুলে চলে যেতে পারি। গেলে দেখা হবে।’
‘স্কুলে যাবেন? কিন্তু দেখা যে হবে না আর-’
‘কেন, ছুটিতে আছ?’
‘না, ঠিক তা না, আবার ছুটিও বলতে পারেন- আচ্ছা, যাই তাহলে।’
জিনিয়ার কথার মানে বুঝলাম না। ছুটির বিষয়টা জানতে চাইব ভাবতেই দেখলাম সে বিরলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। আর কয়েক পা দ্রুত হেঁটে যেতেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখ দেখা না গেলেও আমার কেন যেন মনে হলো জিনিয়ার চোখে পানি ছিল। মেয়েটা কি এত দিনেও আমার প্রতি মুগ্ধতা থেকে বেরোতে পারেনি? কে জানে! বিয়েশাদি করল কি না তা-ও তো জিজ্ঞাসা করা হলো না। রাতের উথাল-পাতাল বাতাস গায়ে মেখে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। কিন্তু পরদিনও জিনিয়ার শেষ মুহূর্তের মুখটা ভাবনা থেকে সরল না। দুপুরের পরপর ভাবলাম, যাই একবার গার্লস স্কুলে গিয়ে জিনিয়ার খোঁজ করি। রিকশা নিয়ে চলে গেলাম গণেশতলায়। স্কুলের দারোয়ানকে তার নাম বলতেই সে চোখ মুছতে শুরু করল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। স্কুলটার স্বাভাবিক যে দৃশ্য তেমন লাগছিল না কেন যেন। শহরের ঠিক মাঝখানে স্কুল বলে গেটের সামনে বরাবর ফেরিওলা, তীর্থের কাকের মতো কিছু ছেলেদের অপেক্ষা, রিকশায় করে কিছু মেয়ের আগমন বা প্রস্থান, সেসব কিছুই দেখলাম না। বুড়ো দারোয়ানের কান্না থামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।
‘স্যার, আজকে তো স্কুল বন্ধ। খোলা থাকিলেও আপনে তারে পাইতেন না গো। দিদিমনিকে ওই যে ওইখানে কালকে ট্রাকে চাপা দিসে। আমি সামনে থাকিও কিচ্ছু করতে পারলাম না। আজকে সেই শোকে স্কুল বন্ধ দিসে।’
রাস্তার উল্টো দিকে দারোয়ানের দেখিয়ে দেয়া জায়গাটার দিকে তাকালাম। কিছু ইট দিয়ে ঘেরা একটা বৃত্ত আর মাঝখানে কিছু গোলাপ আর গাঁদা ফুলের পাপড়ি ছড়ানো। আশ্চর্য তো! তরতাজা মেয়েটা এভাবে- জিনিয়া কাল বলছিল বটে যে ভিড়ের চোটে এই রাস্তায় গাড়ি-টাড়ি সব বেপরোয়া হয়ে গেছে। আর তার পরপরই তার এই অবস্থা হলো, মানা যায়?
‘তা কখন হলো অ্যাক্সিডেন্টটা? ডেডবডি কোথায় এখন?’
‘গতকাল সকালে, দিদিমনি যখন স্কুলে আসতেছিলেন। সন্ধ্যায় শ্মশানে পোড়ানো হইছে কালকে।’
দারোয়ানের কান্নার দৃশ্য দেখতে পেলাম কিন্তু তার শব্দ কেন যেন আর শুনতে পাচ্ছিলাম না। মনে হলো আমার পায়ের নিচে একটা ভূমিকম্প লেগে গেল। দাঁড়িয়ে থাকতে সত্যি আমার কষ্ট হচ্ছিল তখন আমার। দাঁড় করিয়ে রাখা রিকশাটায় কোনো রকমে উঠে বসলাম। সারা শরীরে ঘাম ছুটে গেল মুহূর্তেই। হয়তো টেনশনে রক্তের সুগার হঠাৎ কমে গেছিল কিংবা অন্য কিছু যা আমি ঠিক বুঝিনি। ইশারায় রিকশাওলাকে পেছনে সুইহারির দিকে রওনা দিতে বললাম। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? যতদূর জানি সকাল দশটায় স্কুল শুরু হয়, তখন যদি জিনিয়া অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তবে আমার সাথে তার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দেখা হলো কী করে?
মাথা ঘুরছিল। আমার সত্যিই সুগার কমে গেছে তখন। সারা শরীর কাঁপা শুরু হলো। মোড়ে একটা দোকানের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে দুটো ক্যানডি কিনে মুখে পুরলাম। সামান্য পরে খানিকটা ভালো লাগা শুরু হলো। শরীরের কাঁপাকাঁপি থামলে রিকশাওলাকে রিকশা ঘোরাতে বললাম। কাঞ্চন ব্রিজে যাওয়া দরকার। ব্রিজ থেকে অনেক দূরে শ্মশানঘাটটা দেখা যায়। ব্রিজে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম। সেখানে যখন সে আমার সাথে দাঁড়িয়ে ছিল, ওখানে, ওই শ্মশানে তখন সেই জিনিয়াকেই পোড়ানো হচ্ছিল? কী করে বিশ্বাস করি! সে কি কেবল ক্ষমা চাইতে আমার কাছে এসেছিল, নাকি অন্যকিছু? ক্ষমা চাওয়াটা কি তার এত জরুরি ছিল? শ্মশানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই বুড়ো বয়সে কী যে ভীমরতি হলো আমার, শোঁ শোঁ বাতাসের মধ্যে ‘জিনিয়া` ‘জিনিয়া` বলে চিৎকার করতে লাগলাম। কেন যেন মনে হলো কাল যদি সে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এখানে আসতে পারে, তবে আজ পারবে না কেন?
রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কুয়াশা ঘিরতে থাকা শূন্য ব্রিজের ওপরে বাতাসের ধাক্কায় আমার মুখ থেকে নিঃসৃত জিনিয়ার নাম ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল শুধু।
এই লেখকের আরও গল্প...

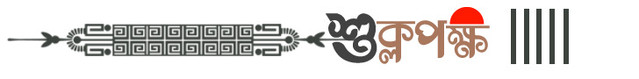








0 Comments