রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রয়াণের মাত্র মাসখানেক আগে ‘মুসলমানীর গল্প’ নামে একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। বলা চলে, এটিই তাঁর জীবনের শেষ ছোটগল্প। তখন অশীতিপর বৃদ্ধকবির জীবনে নানা রোগশোকে কাতরতা নেমে এসেছিল। কিন্তু এই গল্পটির বিষয়শৈলীর প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, বয়সের ভার তাঁকে কর্মের বন্ধন থেকে ন্যূনতম বিচ্যুতি করতে পারেনি। ব্রিটিশ শাসনের পাততাড়ি গোটানোর কালে ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক জ¦রে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। প্রায় হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বসবাসকারী এই দুই বৃহত্তর সম্প্রদায়ের নেতারা তখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের রোমান্টিক দুঃস্বপ্নে বিভোর ছিলেন। প্রয়োজনে এই দুই সম্প্রদায়ের রক্তের উপর দিয়ে হলেও তখন তারা দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাংলার যে-সব নেতা উনিশ’শ পাঁচ সালে কার্জনের বঙ্গভাগের বিরুদ্ধে জীবনপাত করতে প্রস্তুত ছিলেন, তারাও সাতচল্লিশে বাংলাভাগের ব্যাপারে ছিলেন একাট্টা। এমনকি এই ভাগকে কেন্দ্র করে কবিগুরুর প্রয়াণের মাত্র বছর পাঁচেকের মধ্যে কোলকাতাকে ভয়াবহ গ্রেট কিলিং বা দীর্ঘ ছুরির সপ্তাহের সম্মুখীন হতে হয়।
রাজনীতিক মীমাংসা রফা যাই হোক না কেন, বাঙালি কবি সাহিত্যিক ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা এই হিংসা ও হানাহানি পছন্দ করেননি কখনো। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মতো দুই প্রধান শক্তিমান কবি ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ রোধ এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংকট নিরসনে সারাজীবন কাজ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবন সায়াহ্নে এসে উনিশ’শ একচল্লিশ সালের জুন মাসের শেষের দিকে শুভবোধের তাড়নায় লিখলেন ‘মুসলমানীর গল্প’। এই গল্পের প্রতিপাদ্য ছিল—ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ধরন নির্ণয়। এই গল্পে তিনি ভারতবর্ষের অসাম্প্রদায়িক চেতনা নির্মাণে মুসলমানদের অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন। আর জাতির সংকট মুহুর্তে এটি তুলে ধরাই ছিল তাঁর লেখক দায়। মাতৃপিতৃহারা অতিশয় সুন্দরী কমলা ব্রাহ্মণ পিতৃব্যের ঘরে প্রতিপালিত হয়ে আসছিল। বিয়ের পরে প্রতিগৃহে যাওয়ার সময় ডাকাত দলের কবলে পড়ে সে। সেখানে হবির খাঁ নামক এক প্রভাবশালী মুসলিম ধর্মপ্রাণ সমাজনেতার হস্তক্ষেপে ডাকাত দলের লাঞ্ছনা থেকে কমলা মুক্তি পায়। কিন্তু জাত খোয়ানোর অভিযোগে পিতৃব্য গৃহে আশ্রয় জোটে না। তার কাকা-কাকি তাকে ঘরে ফিরে নিতে অস্বীকার করে বলে, “উপায় নেই মা! আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।”
অগত্যা উপায় না দেখে কমলা হবির খাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। প্রথমে কমলা ইতস্তত করলে হবির খাঁ বলেন, ‘বুঝেছি, তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো—যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে।’ হবির খাঁর আট মহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথের কথায়—‘এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপুতানীর মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুতের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন। সে শিবপূজা করত, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাত বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানী এই মহল থেকে যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুণ্ন। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানীর পুত্র।’ হবির খাঁ মায়ের ধর্ম না নিলেও মায়ের প্রতি তার ছিল অফুরন্ত শ্রদ্ধা। কমলা হবির খাঁর ছেলের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে মুসলমান হয়ে যায়। কমলা হবির খাঁকে বলে, ‘বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনো দিন দেখতে পেলুম না।’
এই ঘটনার কিছুদিন পরে কমলার কাকার দ্বিতীয় মেয়ে সরলার বিয়ের পরে একই ঘটনা ঘটে। সেদিন হবির খাঁ ছিল না, কমলায় তার ভার তুলে নিয়েছিল কাঁধে। কন্যাপক্ষরা যখন কন্যাকে পালকির মধ্যে ফেলে রেখে যে যেখানে পেল দৌড় মারতে চায় তখন তাদের মাঝখানে দেখা দিল হবির খাঁয়ের অর্ধচন্দ্রআঁকা পতাকা বাঁধা বর্শার ফলক। সেই বর্শা নিয়ে দাঁিড়য়েছে নির্ভয়ে একটি রমণী।
সরলাকে তিনি বললেন, ‘বোন তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। যিনি কারো জাত বিচার করেন না।’ কাকা-কাকির বাড়িতে বোন সরলাকে ফিরে দিয়ে কমলা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, ‘আমার বোন যদি কখন দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিনি আছে, তাকে রক্ষা করার জন্য।’ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই হলো ভারতবর্ষ, এই হলো হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক। মুসলমান দিদিও রক্তে যেমন হিন্দু বোনের রক্তের সম্পর্ক আছে, তেমন হিন্দু বোনের রক্ষায় মুসলমান বোনের ভূমিকা আছে। তাঁর মতে, হিন্দুর জাতপাতের ছোঁয়াছুয়ির বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে মুসলমানেরা এই ভারতকে মানবিক ভারতের দিকে অগ্রসরে ভূমিকা রেখেছিলেন। এদেশকে গড়তে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, ‘এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।’
রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে আটটি গল্পে মুসলিম অনুষঙ্গ এসেছে। এগুলোর মূল সুর হিন্দু-মুসলিম মিলন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ধর্মের জাতপাতের ছোঁয়াছুঁয়ির আঘাত থেকে মুক্ত ছিলেন না। পঞ্চদশ শতকের শুরু থেকেই তাঁর পরিবার মুসলমানের সংস্পর্শে আসার অভিযোগে হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে পতিত হয়ে সংখ্যালঘুত্ব বরণ করে। তারপর ইংরেজ আসার পরে উনিশ শতকে কবিপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব নিলে তাঁরা পুনরায় সংখ্যালঘুর মধ্যেও সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন। কবির নিজের কথায় ‘আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।’ এসব জাতপাতের বেদনা থেকে তিনি ‘গোরা’ উপন্যাসে বলেছিলেন, ‘‘আপনি আজ আমাকে সেই দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা দিন যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই। যার মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না।’
অনেকে অভিযোগ করে থাকেন, কথাসাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল। বিশেষ করে তাঁর রচিত দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, মৃণালিণী ও সীতারামসহ অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাসে মুসলমান পাঠকগণ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পান। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর কিছুটা সত্য হলেও, তাঁর রচনা এদেশে বসবাসরত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিগত পার্থক্যের প্রকাশ। হয়তো অনেকে বলবেন, বঙ্কিমের আগে প্রায় ছয়শত বছর বাঙালি হিন্দু-মুসলিম দুটি সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করলেও তাদের মধ্যে তেমন কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখা গেল না, অথচ উনিশ শতকের তথাকথিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনের কালে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হলো।
ইংরেজ আসার আগে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম অনুষঙ্গ থাকলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প খুব একটা লক্ষ্য করা যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক আবির্ভাবের প্রায় একশ বছর আগে বাংলার সবচেয়ে শক্তিমান কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের রচনাতে মানসিংহ ও ভবানন্দ উপাখ্যানে জাহাঙ্গীর বাদশাহ’র নাজেহাল দেখা গেলেও সেটা একান্ত রাজায় রাজায় যুদ্ধ। এ দেশে মুসলিম আসার পরে বাংলায় যে ভাষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নির্মিত হয়েছিল, ভারতচন্দ্র তা নিয়ে গর্ব করতেন। তাঁর রচনায় বহুল পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দ ও মুসলিম কেতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটি তার সচেতন প্রয়াসের অংশ। তিনি সাহিত্যে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানী একই সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তার কথায়— ‘না রবে প্রসাদগুণ নাহবে রসাল/ অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।’
স্বাধীন সুলতানী আমলে এদেশের কবিরা মুসলিম রাজা-বাদশার আনুকুল্যে ব্যাপকভাবে বাংলা সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। পূর্ববর্তী সেন রাজারা কাব্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও তাদের রাজ দরবারে বাংলা ছিল অনুপস্থিত। ফলে জয়দেব, ধোয়ী ও বোধায়নের মতো বাঙালি কবিদেরও সংস্কৃতি চর্চা করতে হতো। সুলতানরা যেহেতু বাংলা সংস্কৃতি কোনটাই জানতেন না, সেহেতু পূর্বরাজার ভাষার চেয়ে এদেশে তাদের প্রজাবর্গের ভাষা সাহিত্যের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। আর এভাবেই এ দেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বাতাবরণ খুলে গিয়েছিল। মঙ্গল কবিতায় কিছুটা হিন্দু জাতীয়তাবাদি উপাদানের বাড়াবাড়ি থাকলেও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির নিদর্শন অপ্রতুল নয়। যেমন বিপ্রদাস পিপলাইয়ের ‘মনসাবিজয়’ কাব্যে বেহুলা-লখিন্দরের নিশ্চিদ্র লোহার বাসর ঘরে পুত্রের কল্যাণার্থে মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ কোরআন রেখে দিয়েছিলেন চাঁদ সদাগর। মঙ্গলকাব্যের সময়কালে মুসলিম কবিদের রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোতে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের মিথষ্ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ‘নবী বংশ’ এর রচয়িতা সৈয়দ সুলতান শিব বিষ্ণু ও ব্রাহ্মাকে নবী বলে উল্লেখ করেছেন। ‘ইউসুফ-জুলেখা’ কাব্যগ্রন্থের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যে বালক ইউসুফ হারিয়ে গেলে পিতা ইয়াকুব নবীর পুত্র বিরহের প্রকাশকালে বলছেন, ‘জনে জনে যাব, পুত্র ভিক্ষা মাগব, যে ধর্ম পুত্র ভিক্ষা দেবে সেই ধর্ম গ্রহণ করব।’
আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে মুসলিম সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সঙ্গে পদ্মাবতীর প্রণয়োপাখ্যান হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের নির্দশন। সুফিধারার হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সি হিন্দি ভাষায় এই কাব্য রচনা করেন শারীরিক সম্পর্কবিহীন তীব্র প্রেমের আকুতি হিসাবে। আলাওল মূল পাদুমাবৎকে অনুসরণ করলেও ভাষা ও বিষয়শৈলীতে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত ছিলেন।
গরীবুল্লাহ’র ‘জঙ্গনামা’ গ্রন্থে আমরা দেখি কারবালা যুদ্ধে চন্দ্রভান নামে এক ব্রাহ্মণ মহানবীর দৌহিত্র হযরত হাসানের পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। এই ঐতিহ্যের সম্প্রসারিত রূপ আমরা দেখতে পাই, মীর মশাররফ হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’ উপন্যাসে, যেখানে তিনি আজর নামে এক মূর্তিপূজককে নবী-দৌহিত্রের সম্মান রক্ষায় পুরো পরিবারসহ আত্মত্যাগ দেখিয়েছেন। হোসেনের কর্তিত মস্তকের পরিবর্তে তিনি তার তিনপুত্রের মাথা কেটে সিমারকে দিয়েছিলেন, স্ত্রীসহ নিজেও নিহত হয়েছিলেন। তিনি সিমারের উদ্দেশে বলেছেন, ‘মানুষমাত্রেই এক উপকরণে গঠিত এবং এক ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাতিভেদ, ধর্মভেদ সেও সর্বশক্তিমান ভগবানের লীলা।’
মধ্যযুগে গৌরাঙ্গ শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মতো অসংখ্য কবিরা বহু অমর পদ রচনা করেছেন। এটি হিন্দু ধর্মীয় ভাব আন্দোলন বলে মুসলমান কবিরা দূরে থাকেননি, তারাও রচনা করেছেন রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে অসংখ্য ভক্তি সঙ্গীত। এদের মধ্যে আলাওল, আফজল, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তজা, আলী রেজা প্রধান। তাদের রচনার ভাব ও বিষয় হিন্দু রচিত পদ থেকে কোনো অংশে কম নয়। তাদের রাধা-কৃষ্ণের জীবাত্মা-পরমাত্মার ভাবরসের সঙ্গে ইসলামি সুফিতত্ত্বের দর্শন একাকার হয়ে গিয়েছিল। এটিই ছিল পরবর্তীকালে এদেশে বাউল-সুফি সাধনার সহজিয়া উপায়। যার পথ ধরে লালন, হাসন, রাধারমন, আব্দুল করিমের মতো অসংখ্য সাহিত্য সাধকের প্রকাশ। আর আধুনিকালে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম একাই এ ধারার সকল দীনতা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পদের বিষয় ভাব ও শিল্পের লালিত্বে হিন্দু ভক্তের প্রাণের সঙ্গে মুসলমান রসগ্রাহীর হৃদয়ও আন্দোলিত হয়।
বিশ শতকের সূচনালগ্নে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগে মীর মশাররফ হোসেন ছাড়া উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের পক্ষে শক্তিশালী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। ফলে সাহিত্যে মুসলিম চরিত্র চিত্রণে কিছুটা ঘাটতি পরীলক্ষিত হয়। শত শত বছর পাশাপাশি বসবাসের পরেও দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরকে জানার আগ্রহ তীব্রতর ছিল না। ফলে ভৌগোলিক উত্তরাধিকার অভিন্ন হলেও সংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে নিঃসংশয় ছিল না। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তিনি শ্রীকান্ত উপন্যাসে গহর চরিত্র নির্মাণ করেন। রূপদক্ষ শিল্পির কলমের টানে মুসলমান গহরের সঙ্গে বোষ্টমী কমললতার হার্দিক প্রেমময় সম্পর্ক গহরকেও গোঁসাই পদে উন্নীত করে। যদিও তাদের এই সম্পর্ক সমাজ মেনে নিতে পারে না। অসুস্থ গহরকে সেবা দানের অভিযোগে কমললতাকে আশ্রম ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে যেতে হয়। তবু তাঁর সৃষ্টির ফলে গোড়া হিন্দু ও মুসলমান কেউ খুশি হতে পারেন নি। অনেকে বলেন, এর বিপরীতে শরৎকে ‘বিপ্রদাস’ লিখে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।
আমার মনে হয়, বঙ্কিম উপন্যাসে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের তিক্ততা পরবর্তীকালের লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে চরিত্র নির্মাণে অতিরিক্ত সতর্কতার পাশাপাশি উদাসিনতার জন্ম দিয়েছিল। যদিও বঙ্কিমকের প্রতি হিন্দুর বীর্যবত্তা দেখানোর জন্য মুসলিম চরিত্র কিছুটা হেয় করে দেখানোর অভিযোগ করা হয়, তবু সাহিত্যের বিচারে তা পুরোপুরি সত্য নয়। মীর মশাররফ হোসেনের ‘বিষাদসিন্ধু’ উপন্যাসে মুসলমানদের দ্বারা মুসলমান নিধনের ঘটনা যখন মুসলমান সমাজের প্রতি লেখকের বিদ্বেষভাব হিসাবে দেখা হয় না; তখন বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলমান আকবরের সেনাপতি জগৎসিংহের কাছে কৎলুখাঁর পরাজয়, আয়েষার প্রণয় বিদ্বেষভাবে দেখা হয়। একইভাবে আবুল মনসুর আহমদের বিখ্যাত ‘আয়না’ গ্রন্থের ‘হুজুর কেবলা’ ‘নায়েবে নবী’সহ প্রায় সকল রচনা অন্যধর্মের সাহিত্যিকদের দ্বারা লিখিত হলে মুসলিম সমাজে দক্ষযজ্ঞ বেঁধে যেতো।
বঙ্কিমের শক্তিশালী কলম মুসলমান সাহিত্যিক সমাজের জার্ড্যতা ভাঙার ক্ষেত্রে কাজে লাগলেও তিনি মুলমানদের দুর্দিনে আরো কিছুটা হৃদয়বান হতে পারতেন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তাঁর জন্যও বিষয়টা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। ইংরেজ জামানার উষালগ্নে পরাজিত রাজার নিন্দা এবং বিজয়ী রাজার গুণগান, একই সঙ্গে রাজা ও প্রজার উচিতকর্ম হিসাবে বিবেচিত। সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের ভাগ্য যদিও একই সুতায় বাঁধা ছিল, তবু পূর্বরাজা মুসলমান হওয়ার ফলে মুসলমান প্রজাদের দুঃখের কারণ একটু বেশি ঘটেছিল। আবার উনিশ শতকেই নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়’র মতো হৃদয়বান অনেক কবি-সাহিত্যিক জাতীয়তাবাদি নায়কের খোঁজে সিরাজউদ্দৌলাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন।
বিশ শতকের প্রথমার্ধে কাজী নজরুল তাঁর সাহিত্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলিম মিলনে কাজ করেছিলেন। এমনকি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতভাগ তিনি সমর্থন করেননি। তাঁর নিজের জীবনে তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও জাতধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দু মেয়ের পাণিগ্রহণ করেছিলেন। নিজের পুত্রদের নাম হিন্দু মুসলমানের মিলিত ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। মুসলমানের ধর্মকে নিয়ে তিনি যত গান-কবিতা লিখেছেন, হিন্দুর দেবতাকে নিয়ে তারচেয়ে কম লেখেন নি। তাঁর পরবর্তীকালের কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। কালকাতার গ্রেটকিলিংয়ের সময়ে জীবনানন্দ দাশ ‘১৯৪৬-৪৭’ নামে কবিতায় লিখেছিলেন—
‘মানুষ মেরেছি আমি- তার রক্তে আমার শরীর
ভ’রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ’য়ে বধ ক’রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক’রে ঘুমাতেছি- ...
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ’য়ে
ব’লে যাবে কাছে এসে, ‘ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ-
আর তুমি?’ আমার বুকের ’পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে সুধাবে সে- রক্তনদী উদ্বেলিত হ’য়ে
বলে যাবে, ‘গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালীর-’
অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টি করা হয়। ইংরেজ তাদের শাসন করার মানস নিয়ে এদেশের হিন্দু-মুসলিমকে ধর্মের নামে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ভারত বিভাগের মাধ্যমে সেই ধর্মবিদ্বেষ এখনো এদেশের মানুষ বহন করে চলছে। পাকিস্তানের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদি যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিল না। এ দেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে হিন্দু-মুসলমান একইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আত্মত্যাগ করে।
সম্প্রতি কবি নির্মলেন্দু গুণ সে-সময়ের একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির উদাহরণ দিয়েছেন, ‘‘আমি যখন মেট্রিক পাস করে কলেজে ভার্তি হয়েছি তখন আমার পরিচয় হয়েছিল মহারাজা রোডের বসবাসকারী একজন শিল্পীর সঙ্গে। তিনি ধর্মে মুসলমান ছিলেন, নাম ছিল রশিদ। তিনি চমৎকার প্রতিমা বানাতে পারতেন এবং আমাদের ময়মনসিংহ শহরে তার নির্মিত প্রতিমা দুর্গা, সরস্বতী পূজায় ব্যবহৃত হতো। একবার আমি তার কাছ থেকে একটি সরস্বতী প্রতিমা সংগ্রহ করেছিলাম। তার শিল্পকর্মের প্রতি আমার ভালোবাসা আছে বুঝতে পেরে তিনি আমাকে একটি চমৎকার সরস্বতী প্রতিমা বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন গ্রামে ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না। আমরা হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে স্টেশন থেকে সেই সরস্বতী প্রতিমা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের গ্রামের বাড়িতে। তারপর এটি একজন মুসলমান তৈরি করেছেন জানার পর আমাদের এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মুসলমানরাও এসে এই প্রতিমা দর্শন করেছেন এবং তার সৃষ্টির প্রশংসা করেছেন। তিনি শুধু দেবী মূর্তি তৈরি করতেন এরকম নয়। তিনি অনেক সাধারণ কৃষকের ছবি, প্রমিকের ছবি মৃৎশিল্পের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতেন। তার একটা স্টুডিও ছিল মহারাজা রোডে। এখন এর পাশেই রয়েছে মুকুল বিদ্যানিকেতন বলে একটা স্কুল। .. ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তার স্টুডিওতে হামলা করে এবং যত মূর্তি ছিল সেগুলো ভেঙে ফেলে। সেগুলো রক্ষা করতে গিয়ে রশিদ জীবন দান করেছিলেন।’ (দ্য ডেইলি স্টার, ১৪ অক্টোবর, ২০২১)
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। পাকিস্তান সরকারের উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তান-পর্বের তেইশ বছরের আন্দোলন যেমন ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তেমন ছিল বাঙালির বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরবর্তীকালে এ দেশের রাজনীতিতে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক বিভেদ আবারো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সাহিত্যে তা খুব বেশি প্রকট না হলেও অনেক লেখকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে লেখকরা হয়তো একদিন ভেবেছিলেন একটা দেশের নাগরিক হিসাবে হিন্দু মুসলিম ধর্মগত হিংসা নিরসনে লেখার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মানুষের অন্ধকার প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার কালসাপ এখনো শীতঘুমে আড়মোড়া ভাঙে; সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে আসতে চায়। ফলে মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের মতো এখনো কবি-সাহিত্যিকদের অনেক দিন গাইতে হবে- ‘শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’
লেখক: কবি, লেখক ও গবেষক

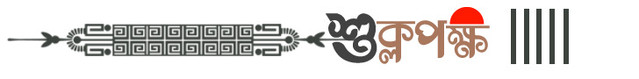









0 Comments