এক
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়েতে কিছুক্ষণ আগে কাতার এয়ারওয়েজের কিউআর৭৬৯ বিমানটি অবতরণ করেছে। কাস্টমস বিভাগের কাজ সেরে কেউ ঘরে ফিরছে আবার কেউ এসে নতুন কাজে যোগ দিচ্ছে। যারা অনেক দিন বাদে দেশে ফিরছে তাদের ঘিরে বাইরে হুইহুল্লোড় চলছে। কোথাও আবার ছোট খাট কান্নার পর্বও চলছে। একটা জটলা সাথে আরেকটা জটলার কোন যোগসাজস নাই। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদযাপন। যে উদযাপনের মর্ম ও আবেগ কেবল উদযাপনকারীরাই বোঝতে পারে। বাইরে থেকে সেটাকে নেহায়েত আদিখ্যেতাও ভাবতে পারে কাঠখোট্টা টাইপের লোকজন। কেউ কেউ আবার বাক্সপেট্রা নিয়ে টেক্সি ধরে নির্বিকার গন্তব্যে ছুটে চলছে। দেশ আর বিদেশ এদের কাছে বিশেষ কোন তফাতার্থক নয়। কাজে অকাজে ঘরের ভিতর-বাহির করার মতো দেশ-বিদেশ করাও যে এদের মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; সেটা এদের ভাবলেশহীন গতিবিধি দেখলেই বোঝা যায়।
ইভান দুই বছর পর দেশে ফিরছে। যদিও দেশে ফেরার আলাদা কোন অনুভূতি জাগছে না। নিজেকে অনেকটা পানির মতো মনে হচ্ছে। যখন যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। ইভানও তাই হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। শুধু পরিবার-পারিবারিক আবহটাই যা একটু মিস করেছে। আরও একটা জিনিস মিস করেছে, ঢাকার রাস্তার পাশের দোকানে দাঁড়িয়ে চা পান করাটা। তাছাড়া বিশেষ কোন অভাব অনুভব করেনি বিদেশ বিভূঁইয়ে। পড়াশুনার চাপ আর কাজের ব্যস্ততা তাকে ব্যস্ত রেখেছিল। কোন কিছুর অভাব বোধ করবার সময়ই দেয়নি। এটাই বোধ হয় তফাৎ বাংলাদেশ আর উন্নত বিশ্বের মধ্যে। জাপানের একটা জরিপে দেখেছিল-সত্তর ভাগ জাপানি গত একমাস তাদের সঙ্গীর সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়নি। বলা ভালো কাজের চাপে সময় করে উঠতে পারেনি। তাই হয়তো তারা উন্নত বিশ্ব-আর আমরা উন্নয়নশীল। জামা-কপড় বুনে আর নির্মাণ শ্রমিক হয়ে বিদেশে যাই। রেমিটেন্স পাঠাই। কিন্তু একটা দেশ আর কতোদিন এভাবে জামা-কাপড় বুনে তাঁতির মতো চলবে? স্বাধীনতার এতো বছর পর নিশ্চয় তাদের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পথে হাঁটতে হবে। নয়তো স্বাধীনতার সুফলটা কোথায়। তফাৎ কোথায় ব্রিটিশ উপনিবেশ আর পাকিস্থানি শোষণের? তবে আশার কথা হলো প্রযুক্তিগত ভাবে এগুচ্ছে। দুএক জন হলেও এখন গুগল-অ্যামাজনের মতো প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছে। এটাই আশার কথা। যতো যাই কিছু ভাবনায় আসুক, দেশ দেশই। কিছু তো একটা ভালো লাগা কাজ করছেই। তাই এতোদিন পর দেশে ফেরার পর এমন একটা সংক্ষিপ্ত কান্না পর্বের উদযাপন হলে মন্দ হতো না। কেমন একটা “সিনামাটিক থ্রিলিং” কাজ করতো সেটা দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে ছোট ছোট জটলা আর কান্না পর্ব বারবার ঘুরেফিরে দেখছিল।
বিমান বন্দরের বাইরে অব্দি চলে এলো অথচ পরিবারের কাউকেই চোখে পড়ছে না। টার্মিনাল দুইয়ে ভিড় ঠেলে দৃষ্টি সীমার মধ্যে উঁকিবুঁকি করে হতাশ হতে হলো। শেষে আশ্চর্যজনক ভাবে আবিষ্কার করলো তাকে নিতে বিমান বন্দর অব্দি কেউ আসেনি। বাবা না হয় ব্যস্ত মানুষ, ব্যবসা, রাজনীতি,সামজিক কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত-ভাইয়া তো আসতে পারতো কিংবা মা। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তার আগমন কারও ভিতর কোন টান জাগাতে পারেনি। তাইতো প্রাত্যহিক কাজকর্ম সবার কাছে মুখ্য হয়েছে আর ইভান থেকে গেছে গৌণ। সংসার বড় বিচিত্র জায়গা। এখানে কে কখন মূখ্য আর কে কখন গৌণ হয়ে পড়ে সেটা বড় চিন্তার বিষয়। কারও কাছে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততির চেয়ে টাকা, যশ-খ্যাতি হয়ে ওঠে মূখ্য আবার কারও কাছে বিপরীতটা। কেউ যশ-খ্যাতির জন্য আপনজনকে হত্যা করে কিংবা প্রতারণা করে সিংহাসনে ওঠে আবার কেউ আপনজনের জন্য সিংহাসন ছাড়ে। এতো সব ভাবতে ভাবতে কেউ একজন খপ করে হাতটা ধরে ফেলল। চমকে ওঠে তাকাতেই দেখল সিরাজ চাচা। বয়সের ভারে বলিরেখা পড়া ত্বক কুচকে যাওয়া না কামানো কাঁচা পাকা দাড়ি-গুফের রুক্ষ মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাটাকে কসরত করে টিকিয়ে রেখেছে। অগত্য শোধ দেবার দায় থেকে পালটা হাসি ফেরত দিয়ে সিরাজ চাচার সাথে গাড়ির দিকে হাঁটা ধরলো। টুকটাক কথা চললো। কেমন আছে, কি খেয়েছে,আসতে সমস্যা হলো কিনা, ঢাকা অনেক বদলে গেছে-এইসব। বেশির ভাগেরই হা-হুতে জবাব দিলো ইভান। সিরাজ চাচাই যা বকবক করতে থাকলো।
কত পরিকল্পনা ছিল দুই বছর পর দেশে ফিরছে। কই তাকে ঘিরে হইহুল্লোড় পড়ে যাবে, মা চোখে মুখে খুশির ঝিলিক নিয়ে জড়িয়ে ধরবেন, ছোট বোন তিরানা সেলফি তুলবে বলেছিল, কত পরিকল্পনা ছিল,ধুর! বাবা না আসুক, তাই বলে মা তো আসতে পারতো। মা মিস করবে কেন? বাসায় ফিরতেই ইচ্ছে করছে না। শাহবাগ ঘুরে আসবে নাকি? ধানমন্ডি নয়তো সংসদ ভবন? থাক না একটু বাসায় চিন্তায়। কিন্তু বেরসিক আর কাঠখোট্টা সিরাজ চাচা কিছুতেই কোথাও যাবে না। বাসার রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা ধরেলেই তার চাকরি থাকবে না বলে বাবা কড়া হুমকি দিয়ে দিয়েছে।
ও’হেরা ইন্টারনেশন্যাল এয়ারপোর্টেও তাকে কেউ সী অফ করতে আসেনি। নিকলি এখন ফোন রিসিভই করে না। মাঝে মাঝেই ফোন সুইচড অফ করে রাখে। কারণ ছাড়াই ইদানিং ফোন অফ করে রাখে। মেয়েরা এই থিউরিটা খুব প্রয়োগ করে। ফোন বন্ধ করে রেখে নিজের উপযোগিতা যাচাই করে। ফোন বন্ধ রাখলে কেউ যে বারবার ডায়াল করে তাকে পাবে না; তার জন্য উদ্বিঘ্ন হয়ে উঠবে; এটা ভাবতেই তাদের ভালো লাগে। নিজের কাছে নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সমাজে সেও যে গুরুত্বপূর্ণ, তারও যে কর্তৃত্ব ফলানোর জায়গা আছে সেটা ভেবেই আহ্লাদিত হয়, আত্মিক তৃপ্তি পায়।
সিরাজ চাচা খুবই বিশ্বস্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিফৌজরা তার বাবাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। তারপর বাবাই তাকে ড্রাইভারের চাকরি দেয়। দাদা পাকিস্তান আমলে মুসলিমলীগে মন্ত্রী ছিলেন। তার সাথে সিরাজ চাচার বাবা মুসলিমলীগ সমর্থক তারা চাখলাদারের ঘনিষ্টতা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় সিরাজ চাচার বাবা তারা চাখলাদার আল-বদর বাহিনীর কমান্ডার ছিল। নবাবপুরে যাকে পাকি তারা বলে চিনে।
একটা ডকুমেন্টারিতে দেখিয়েছিল কি নৃশংস অত্যাচার করতো পাক বাহিনী। আর তাদের সাহায্য করতো রাজাকার-আল বদররা। মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করেতো, নির্যাতনে কেউ কেউ মারা যেতো, তবুও বেশির ভাগই মুখ খোলতো না। অত্যাচার সহ্য করতো মরে যেতো কিন্তু মুখ খুলতো না। কি দেশ প্রেম থাকলে এটা সম্ভব! ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মুক্তিফৌজদের নখ তুলে ফেলতো, চোখ উপড়ে ফেলতো, হাত-পা ভেঙ্গে দিত, বিবস্ত্র করে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখতো। আর মুক্তিফৌজদের চিনিয়ে দিতো আল বদর, আস সামস, রাজাকাররা। পাকিস্তানী সেনাদের খুশি করতে এলাকার যুবতি মেয়েদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেতো, হিন্দু পরিবার থাকলে তো কথাই ছিল না। নৃশংস ভাবে ও বিকৃত ভাবে তাদের যৌন নির্যাতন করতো পাক বাহিনী। বাড়ি ঘর লুট করতো আগুন দিত রাজাকার, আল বদররা। যুদ্ধের যত ঘৃণ্য কৌশল আছে সবই তৎকালীন পাকিস্তানি জান্তা সরকার প্রয়োগ করেছিল। যুদ্ধের অন্যতম একটা আপকৌশল হলো, নারীদের নির্যাতন করলে বিদ্রোহী জাতি দমে যায়। সেই পথেই হেঁটেছিল পাকিস্তানিরা। কিন্তু বাঙালির মধ্যে যে প্রকট জাতিসত্তা গড়ে ওঠেছিল-স্বাধিকারের যে তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়েছিল তার কাছে কোন কৌশলী টিকতে পারেনি। সব অপকৌশল আর কূটচালকে ছিন্নকরে করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। পত্র-পত্রিকায় এসব ঘটনা পড়েছে ইভান। বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথেও জড়িত ছিল তারা চাখলাদার ওরফে পাকি তারা। প্রথম আলোর এক রিপোর্টে দেখেছিল ইভান। পাকি তারার নামে সেই রিপোর্টে লিখেছিল, সে নাকি বেছে বেছে হিন্দু নারীদের ধরে এনে তার আরদে বন্দী করে নির্যাতন করতো।
এসব সত্যি কিনা তা জানতে একবার সিরাজ চাচাকে জিজ্ঞেস করেছিল ইভান। সিরাজ চাচা এসব মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে শোন ইভান, আমার বাবা ব্যবসায়ী মানুষ ভি আছিলো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো, ধার্মিক, শিল্পমনা, জনদরদী, সমাজ সেবক। শ্যাম বাজারে মছলার আরদ আছিলো। এলাকায় তার একটা ছুনাম আছিল। নবাবপুর, শ্যাম বাজার, ইসলামপুরের হগলতে তারে এক নামে চিনতো। তার নামে কলঙ্কভি দিতেই এই ছব প্রচার করর্যা বেড়ায় মানইছেরা। স্বাধীনতার পর শত্রুপক্ষ বাবাকে মাইরা বুড়িগঙ্গায় ভাছাইয়্যা দিছে। আরদে আগুন দিয়্যা জ্বালাইয়া দিছিলো। তহন স্যার আমারে চাকরীভি দিছে। বাবা যুদ্ধের সুময় শান্তি কমিটিতেভি আছিলো এ কথা মিছা না, হাছা। তয় সে কোন আকাম কুকাম করে নাইকাভি। দেশ বাঁচানোর জন্যভি সে চেষ্টা-তদবির করছে। পাকিস্তানের লগে এক থাহনের লাইগাই বাবা চেষ্টাভি করছে। কও কামড়ি কি খারাপ করছে নাহি? এই যে দেহ ভারত এহন চুদুরবুদুর করে পাকিস্তানের লগে থাকলে কি এডি করবার পারতো? হান্দাইয়া দিতো না? পঁয়ষট্টির যুদ্ধের কথা হুননাইক্যা? পাছার মধ্যে লেঙ্গুর হান্দায়া দৌঁরাইছিলো। যাইগ্যা হিডি আর কইয়া কাম নাই। তুমি কইলাম এইছব আলতু-ফালতু কতায় কান দিয়ো না।
দেশে থাকতে একবার নবাবপুর গিয়েছিল ইভান। প্রথম আলোর রিপোর্ট কতটুকু সত্য খোঁজ নিতে। নবাবপুরে কি আসলেই পাকি তারার অস্তিত্ব ছিলো কিনা। সেখানে গিয়ে এক রোমহর্সক ঘটনার সন্ধান পায় ইভান। পাকি তারার হিন্দু নারীদের প্রতি আসক্তি ছিল। যুদ্ধের সময় এলাকার অনেক শিশু, যুবতি এমনকি বৃদ্ধা হিন্দু নারীদের পর্যন্ত ধরে নিয়ে তার আরদে নির্যতন করতো। পাক বাহিনীর হাতে তুলে দিতো। ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করতো। স্বাধীনতার পর যখন মুক্তি বাহিনীর তার শ্যাম বাজারের আরদে আগুন দিতে যায় তখন সবচেয়ে বর্বর ঘটনাটি উন্মোচিত হয়।
শাঁখারী বাজারের নাম ডাক ওয়ালা স্বর্ণব্যবসায়ী কিরণ মিত্র বিয়ে করেছিল কলকাতার বড় বাজারের বিখ্যাত জুয়েলারি মালিক রতন মিত্রের বড় মেয়ে পৌষালী মিত্রকে। রূপে গুণে পৌষালী মিত্র ছিলো নজর কাড়ার মতো। নিটোল মুখশ্রী, শান্ত কাল দুটি চোখ ঠিকরে পড়া দৃপ্তিময় চাহনি, পাতলা গড়ন,নারী সুলভ সকল ঢেউ খেলে যেতো দেহে। একবার চোখ পড়লে চোখের আড়াল হওয়া অব্দি কেউ আর চোখ ফেরাতে পারত না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে যাওয়ার পথে পাকি তারার লোকদের হাতে সোয়ারীঘাটে পরিবার সমেত ধরা পড়ে যায় কিরণ মিত্র। স্বর্ণালঙ্কার, টাকা পয়সা আর পৌষালী মিত্রকে রেখে বাকি পরিবারকে জাহাজে তুলে দেয় পাকি তারার বাহিনী। সেই পৌষালীকে ধরে নিয়ে আসে তারার আরদে। ভিতরের কুঠরীতে আটকে রেখে যুদ্ধের পুরো সময় নির্যাতন করা হয় পৌষালী মিত্রকে। ডিসেম্বরের প্রথম প্রহরে মৃতপ্রায় পৌষালীকে মুক্তিফৌজরা উদ্ধারের পর এসব তথ্য উন্মোচিত হয়।
বীভৎস সেই নির্যাতনের বর্ণনা তখন ইত্তেফাকে ছাপা হয়েছিল। বিশ্ব মিড়িয়ায় কল্যাণে ঐ ঘটনা তোলপাড় তুলে দেশে দেশে মানুষের মনে সহানুভূতি জাগিয়েছিল। পৌষালীকে পুরো যুদ্ধের সময় শাড়িহীন পেটিকোট-ব্লাউজ পরিয়ে রাখা হয়েছিল। যাতে করে গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে আত্নহত্যার চেষ্টা না করতে পারে। যুদ্ধের শেষে যখন মুক্তিফৌজরা তাকে উদ্ধার করে তখন তার শরীরের পোষাক শতছিন্ন। মুক্তিফৌজরা নিজের গাঁয়ের জামা খুলে তার আব্রু রক্ষা করেছিল। ইত্তেফাককে পৌষালী বলেছিল তাকে একাধিকবার একাধিক মানুষ এসে নির্যাতন করতো। এমনকি নারীর বিশেষ অসুস্থতার দিনগুলোতেও মুক্তি মিলতো না। সে সময় মেঝে রক্তে ভেসে যেতো। তিনি নিজেই সেই অসুস্থ শরীরে তা পরিষ্কার করতেন। ঘুমানোর জন্য কোন বিছানা ছিলনা। মেঝেতে পড়ে থেকে ঘুমাতে হতো পৌষালীকে।
প্রথম দিকে কিছুতেই সেই ঘটনার সাথে খাপ খাইতে পারেনি পৌষালী। পরে নিয়তি মেনে নিয়েছিল। যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই মুক্তির আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে। কয়েক মাস পর সে মুক্তির আশা একেবারের ছেড়ে দেয়। তখন প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে। সেই সময়ের পিশাচদের কতো মিনতি করতো যেন তাকে মেরে ফেলা হয়। গোসলও করতে পারতো না ঠিক ভাবে। একটাই পোষাক ছিল। গোসল করতে হলে ভয়ে ভয়ে সেটাই পরিষ্কার করে দিয়ে বিবস্ত্র থাকতে হতো। তাই তিন দিন সাত দিন পর গোসল করতো। পরে ইত্তেফাকের সহায়তায় পৌষালীকে কলকাতায় তার স্বজনদের কাছে পাঠানো হয়।
সেই পাকি তারার ছেলে সিরাজ চাচা। তাকেই বাবা ডেকে এনে ড্রাইভারের চাকরি দেয়। যুদ্ধের পর তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়, সম্পত্তি সব লুট করা হয়। বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে একদিন আমাদের বাড়িতে আসে। তখন তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন বাবা। সেই থেকে আজও আমাদের সাথেই আছেন। প্রচন্ড প্রভু ভক্ত সিরাজ চাচা। তাই বাবাও তাকে বিশ্বাস করেন। হয়তো বাবা না আসতে পেরে বিশ্বস্ত সিরাজ চাচাকেই পাঠিয়েছেন।
এয়ারপোর্ট রোডের চেহারাটাই বদলে গেছে। কেমন সাজানো গোছানো। দুই পাশে রকমারি গাছ, পায়ে হাঁটার রাস্তাও বেশ চওড়া আর ঝকঝকে ব্লকে বাঁধানো, তারপর রেল লাইন, এরপর লেক। কেমন সাঁইসাঁই করে একেকটা গাড়ি ছুটে চলছে। দেখেই মনটা ভালো হয়ে গেল। আহ স্বদেশ। কুড়িল ফ্লাইওভার চালু হয়েছে। রাস্তার চেহারাটাই পাল্টে গেছে। এখন বিশ্বরোড সিগন্যালে বিরক্তিকর বসে থাকতে হয় না। যে যার গন্তব্যে ছুটতে লেন ধরে। ক’বছরে ঢাকা এতোটা পাল্টে গেলো! ভাবাই যায় না। চমৎকার।
কাকলী সিগন্যালে এসে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। সারিসারি মানুষ রাস্তা পার হচ্ছে। পুরুষ-মহিলা, বাহারি তাদের সাজ-পোষাক। যে যার গন্তব্যের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটছে। মহিলাদের বড় অংশই পোশাক শ্রমিক হবে। এদের বাহ্যিক সাজসজ্জা আর আদব কেতা দেখলেই বলে দেওয়া যায়। দেশের অর্থনীতিই দাঁড়িয়ে আছে এই সব খেটে খাওয়া মানুষের ওপর। ইভান একটা জিনিস লক্ষ্য করলো অনেক কিছুই বদলালেও ঢাকার মানুষের আগের সেই মানসিকতা বদলায়নি। পাশের ফুটওভার ব্রিজ রয়েছে। কিন্তু খুব কম মানুষই সেটা ব্যবহার করছে। শহরের উন্নয়নের সাথে সাথে নাগরিকদের মানসিক উন্নয়নও হওয়া প্রয়োজন। নয়তো একটা দেশ এগোয় না। আমেরিকাতে কেমন নিয়ম মেনে চলে মানুষ। কি রাস্তা পারাপারে, কি শহরের পরিচ্ছনতা রক্ষায়। যে ইভান দেশের যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলত সেই একদিন বোঝতে পরল যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা অন্যায়। অথচ দেশে থাকতে সেই বোধ তার জাগ্রত হয়নি। পরিবেশ অনেক কিছুই মানুষকে শিক্ষা দেয়। এদেশেও সেই পরিবেশ গড়ে ওঠা দরকার। কিন্তু কতদিনে গড়ে ওঠবে সেটাই প্রশ্ন।
গাড়ির গ্লাসে টোকার শব্দে চেয়ে দেখে উস্কো খোসকো চেহারা, এলোমেলো চুলের ছোট এক মেয়ে-ততোধিক ছোট বোনকে কোলে নিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে সাহায্য চাচ্ছে। সামনে এক মলিন আশিতিপর বৃদ্ধাকে লাঠিতে ভর দিয়ে সাহায্যের জন্য গাড়িতে গাড়িতে ঘুরতে চোখে পড়লো। ঢাকার এই ভিক্ষুকের পরিস্থিতিটা বোধ হয় পাল্টায়নি। দিন দিন ঢাকা নতুনে ঢেকে যাচ্ছে-ভিক্ষুকের আনাগোনাও বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে উন্নয়নের সুফল সমাজের সকল স্তরে পৌঁছাচ্ছে না। উন্নয়ন যে সুষম হচ্ছে না-অর্থিক বৈষম্য দিনকে দিন বেড়ে চলছে-এই তথ্যটা বোঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়ার দরকার হয় না। প্রান্তিক উন্নয়ন না করে সারা বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির তত্ত্বে এগিয়ে চলছে। সেদিন কোন একটা রিপোর্টে দেখল বিশ্বর অর্ধেক সম্পত্তি এক শতাংশ মানুষের হাতে। এতে কি মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে না? এই দায় কে নিবে? এটা যে একটা দায় সেটাই বা কে বোঝাবে। কল্যাণ রাষ্ট্র বলে কি সত্যি পৃথিবীতে কিছু আছে? ইভানের মনটা হঠাৎ বিস্বাদে ছেয়ে গেল-ক্ষাণিক আগের এয়ারপোর্ট রোডের সেই ভালোলাগাটুকুর লেশ মাত্র আর অবশিষ্ট রইলো না। গ্লাস নামিয়ে ইভান জিজ্ঞেস করলো-টাকাতো নেই, ডলার নিবে? ইভানকে চমকে দিয়ে মলিন সেই শিশুটিই প্রচ্ছন্ন হাসি মাখা মুখে স্বীকারুক্তিমূলক প্রতি জিজ্ঞাসায় বললো-কয় ডলার দিবেন? দেন ভাঙ্গাইয়া নিমুনে। সিরাজ চাচা ক্ষেপে গিয়ে শিশুটিকে সজোরে একটা ধমক দিয়ে বললো-ভাগ এইহান থিকা। সাবধান ইভান, ওরা একেকটা খচ্চরের হাড্ডি। ওদেরকে কোন ডলারভি দিবা না। বলতে বলতে নিজের পকেট থেকে দশ টাকা বের করে দিল। ততোক্ষণে সিগন্যাল ছেড়ে দিয়েছে। সিরাজ চাচা ঘরঘর শব্দে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।
দুই
তত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতার প্রশ্নে সৃষ্ট জটিলতায় আওয়ামীলীগ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে টানাপোড়েনের মধেই বিএনপি মনোনীত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ রাজনৈতিক দল এবং সুশীল সমাজের সাথে কোন রকম আলাপ আলোচনা ছাড়াই নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ঘোষণা করে। কারণ হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের অন্য বিকল্পগুলোতে সর্বোদলীয় ঐক্যমত্য না থাকায় নিজেকেই প্রধান হিসেবে ঘোষণা করার কথা বলেন। ফলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও সমান সুযোগ নিশ্চিতে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। আওয়ামীলীগ নের্তৃত্বাধীন প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক জোট মহাজোটসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলো তা মেনে নেয়নি। বিএনপি জোটের বাইরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং তারা যুগপদ আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ জরুরী আইন জারি করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার অবিশ্বাস ও দূরত্ব কমাতে তত্বাবধায়ক সরকারের মোড়কে সেনা সমর্থিত অন্তরবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন বিশ্বব্যাংকের সাবেক পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফকরুদ্দীন আহমদ। পেছনে থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন সেনা প্রধান জেনারেল মঈন উদ্দিন আহমেদ।
তবে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টার ভাষ্যমতে এতোটা সরল ছিল না ক্ষমতা হস্তান্তর। এতোটা সহজে ক্ষমতা ছাড়েননি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উদ্দিন আহমেদ সশস্ত্র ভাবে বঙ্গভবেন প্রবেশ করেন। যদিও রাষ্ট্রপতির বাসভবন সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকা। নিঃছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় সেখানে। কোন বাহিনী প্রধান কিংবা মন্ত্রীরাও তাদের নিরাপত্তা রক্ষী বিহীন নিরস্ত্র হয়ে বঙ্গভবনে প্রবেশ করতে হয়। সেখানে কি ভাবে জেনারেল মঈন সশস্ত্র ভাবে বঙ্গভবনে প্রবেশ করে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছিলেন সেটা অবশ্যই ভাবনার বিষয়। ধারণা কওয়া হয় অস্ত্রের মুখেই সেদিনের রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেছিল সেনাবাহিনী। এটাও জনশ্রুতি আছে যে সামরিক শাসন জারি করতে চেয়েও জেনারেল মঈন আন্তর্জাতিক চাপে তা করতে পারেননি। জাতিসংঘ নিশ্চয় কোন সামরিক হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক দেশের ওপর মেনে নিতেন না। তাছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করে। বিপুল সংখ্যক সেনা সদস্য দেশের ভাবমূর্তী ও অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক শাসনের মতো পরিস্থিতিতে সেই সেনা সদস্যদের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরী হতো এতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থনীতি তো জড়িত ছিলই। এতোকিছু বিবেচনায় নিয়ে জেনারেল মঈন আর রাষ্ট্র ক্ষমতা সরাসরি দখল না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ানোর কৌশল নিলেন।
সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর ক্ষমতায় থাকার পর নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। সেচ্ছায় স্বপ্রণদিত হয়ে নির্বাচন দিয়েছে বিষয়টা তেমন নয়। দুর্নীতি দমন, বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা আর মাইনাস টু ফর্মুলা হাতে নিয়ে মাঠে নামে অনির্বাচিত অন্তরবর্তীকালীন সরকার। পাকিস্তানে যেমনটা করা হয়েছিল বেনজির ভুট্টু ও নেওয়াজ শরীফের ক্ষেত্রে।
বিচার বিভাগকে প্রসাশন থেকে আলাদা করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ফিরেয়ে দিয়ে প্রথম ধাপ উতরে যায়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানও এগিয়ে চলে। কিন্তু মায়নাস টু পরিকল্পনায় এসে আটকে যায় ফখরুদ্দীন-মইন উদ্দিনের স্বৈরতান্ত্রীক সরকার। বিএনপি-আওয়ামীলীগকে ভেঙতে সংস্কারপন্থী নামে দলীয় কিছু নেতা কাজ করে। দলের বেশ ক্ষমতাবান ও ঝানু নেতাদেরকেও এই সংস্কারপন্থীদের দলে দেখা যায়। তাদের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন মানুষের মনে একটা প্রশ্ন তৈরী করে কেন এই অসমর্থিত সরকারের ইশারায় সংস্কার। প্রয়োজন হলে দলীয় ফোরামে কেন এই কথা তুলছে না? রাজনৈতিক কর্মকান্ড সংকীর্ণ ঠিক আছে-তবে নিশ্চয় একদিন প্রকাশ্য রাজনীতি করার পরিবেশ ফিরে আসবে। সংস্কারপন্থী নেতাদের কথা তৃণমূল নেতা-কর্মীদের প্রভাবিত করতে পারলো না।
তৃণমূল পর্যায়ে নেতা-কর্মীদের সমর্থন না পেয়ে দলীয় সংস্কার চেষ্টা ব্যার্থ হয়। বানের পানির তুমুল তোড়ে পিঁপড়া যেমন দল বেধে দলা পাকিয়ে চলে ঠিক তেমনি ভাবে উভয় দলের নেতা-কর্মীরা দলীয় প্রধানের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এক থাকলো। কোন ভাবেই দলকে ভেঙে মাইনাস টু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেল না। দলকে উজ্জীবিত রাখার মতো কোন দলীয় কর্মকান্ড চোখে না পড়লেও দলগুলো ঠিকই টিকে গেলো। সদ্য ক্ষমতার বাইরে যাওয়া বিএনপির মন্ত্রী-সংসদ সদস্য ও নেতাকর্মীরা দুনীতির দায়ে অভিযুক্ত ও বিচারের সম্মুখীন হলেও দলে বড় ধরনের কোন ভাঙ্গন দেখা না দেওয়ায় অনেকই বিস্ময় প্রকাশ করলো। অনেকের ধারণা ছিল সেনা শাসক হিসেবে ক্ষমতায় থাকাকালীন জিয়ার গড়া দল বিএনপি। অন্য দল থেকে মতাদর্শ পরিবর্তন করা নেতাকর্মী আর সুবিধাভোগীদের নিয়ে গড়া বিএনপির সঙ্গগঠনিক ভিত্তি যথেষ্ট দুর্বল অনুমান করে অনেকেই ভেবেছিল হয়তো বিএনপি আর টিকবে না। মানুষের সেই ভাবনার বিপরীতে আশ্চর্যজনক ভাবে বিএনপি এবারের মতো ঠিকই টিকে গেলো।
টিকে যাওয়ার একটা কারণ বোধ হয় দলটির প্রতি খালেদা জিয়ার নিবেদিত প্রাণ ও তার পরিশ্রম। আশির দশকে স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং অনমনীয় মানসিকতা তখনকার প্রজন্মের মধ্যে একটা আদর্শ ও নীতিবোধের জন্ম দিয়েছিল। দলের প্রতি সেসব নেতা-কর্মীদের দায়বদ্ধতা এবং তাদের হাতে গড়া পরবর্তী প্রজন্মের নেতা-কর্মীরা দলের প্রতি অনুগত ছিল। তাই হয়তো বিভিন্ন দল থেকে আসা সুবিধাবাদীদের নিয়ে দল গড়ে উঠলেও এই দুঃসময়েও দলটি টিকে গেল। তাছাড়া আওয়ামী ঘরানার বাইরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বিএনপি ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মঞ্চ নেই বললেই চলে। বিএনপি টিকে যাওয়ার এটাও একটা বড় কারণ হয়ে থাকবে। এর বাইরে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ দেশের বড় একটা অংশ গ্রহণ করেছে। হয়তো সেই জাতীয়তাবাদের শক্তিই জাতীয়তাবাদী দলকে টিকিয়ে রাখলো।
সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ থেকে আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকে রয়েছে। সেটা অনুধাবন করেই প্রত্যকটি রাজনৈতিক দল ছাত্র সংগঠনকে শক্তিশালী করেছে। নিজেদের আদর্শ ও রাজনৈতিক ইচ্ছা ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে কাজ করেছে। আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক ইতিহাস দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলায় ছাত্র সংগঠনের পরিচর্যায় তাদের বিশেষ ভাবতে হয়নি। তবে স্বাধীনতার পর জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দল গঠন করেই বোঝতে পেরেছিলেন ছাত্র সংগঠন ছাড়া দলকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যাবে না এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। তাইতো শুরুতেই তিনি জাতীয়তাবাদী ও বাংলাদেশি আদর্শের বার্তা নিয়ে ছাত্রদের কাছে গিয়েছিলেন।
সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা, পাকিস্তানি আমলের সামরিক শাসন ফিরে আসা ও আওয়ামীলীগের বড় রকমের পতনের পরপরই ছাত্র সমাজ জিয়াকে মেনে নিতে পারেনি। তাইতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে জিয়াকে অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। ছাত্ররা জিয়ার সামনেই প্রতিবাদ করে। দেশের সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতিকে ধাক্কা দেওয়া হয়। এমনকি রক্তাক্ত হতে হয়। কিন্তু জিয়া জানতেন কি ভাবে পরিবেশ নিজের অনুকূলে নিতে হয়। সেদিন টিএসসিতে শিক্ষকদের অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ডেকে এনে ছাত্র-শিক্ষদের কথা ধৈর্যের সাথে শুনে সমাধানের আশ্বাস দেন। সেনা শাসকের মোড়ক থেকে বেরিয়ে গণতান্ত্রিক, জনগণের অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক ধারায় ফিরতে চাওয়া এবং তার ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব ছাত্রদের বড় একটা অংশকে আকৃষ্ট করেছিল। যদিও তার বিরুদ্ধে রাজাকারদের পুনর্বাসন এবং মুক্তিযোদ্ধা সেনাদের বিচারের আড়ালে হত্যার অভিযোগ ছিল কিন্তু তার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, পররাষ্ট্রনীতি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অচিরেই ছাত্রদের বড় একটা অংশকে আকৃষ্ট করে। জিয়ার দেখানো পথেই হাঁটতে চেয়েছিলেন স্বৈরশাসক এরশাদ। তবে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেও ছাত্রদের কাছ থেকে সাড়া পাননি।
ইতিহাস থেকে ভালো পাঠই নিয়েছিল সেনা সমর্থিত তত্ত্ববধায়ক সরকার। রাজনৈতিক কার্যক্রম সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত থাকলেও তারা জানতো ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত রাখা না গেলে তুরুপের তাস উল্টে যেতে পারে-যে কোন সময় পরিস্থিতি পাল্টে যেতে বাধ্য। সেই চিন্তা থেকেই হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী সেনা ছাউনি স্থাপন করা হয়। সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত ছিল। এরই মধ্যে ঘটে গেল এক অপ্রীতিকর ঘটনা। কোন এক সেনা সদস্য কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ছাত্র নিগৃহীত হওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি হঠাৎ পাল্টে যায়। সীমিত কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং নিজেদের গ্রেফতার আতঙ্কে রাজনৈতিক নেতারা চুপ থাকলেও ফুঁসে ওঠে ছাত্ররা। তাদের সাথে যুগ দেয় শিক্ষকরাও। রাজনীতি সংকীর্ণ থাকলেও অনেক রাননৈতিক নেতার সমর্থন ও সহযোগীতা পায় ছাত্ররা। ফলে দানা বাঁধতে থাকা আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সেনা ছাউনি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় সরকার। হয়তো এটাই ছিল সরকারের পিছু হটার শুরু।
সংস্কারপন্থীদের দিয়ে কিছু করতে ব্যার্থ হয়ে নোবেল বিজয়ী ড. ইউনুসের গ্রহণযোগ্যতা আর আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তীকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হল। দল গঠন ও রাজনীতিতে সক্রিয় হবার ইচ্ছা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে সারা দেশে লিফলেট ছড়িয়ে দেওয়া হলো। লিফলেট-পোস্টারগুলো ঠিক ড. ইউনূসের কাছ থেকে বা তার অনুমতিতেই ছড়াচ্ছিল কিনা তা না জানা গেলেও জনগণের প্রতিক্রিয়া ঠিকই জানা গেল। নতুন দল গঠনের ঘোষণা দেবার পরপরই বিস্ময়কর ভাবে ড. ইউনুসের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে লাগলো। ঠিক কতটা জনপ্রিয় তিনি ছিলেন তার কোন মাপকাঠি না থাকলেও-দল গঠন ও নির্বাচনের ঘোষণা দেবার পর পরই তিনি যে সুশীল সমাজে ও জনগণের মধ্যে নিন্দিত হতে লাগলেন একথা স্পষ্ট। শহরে থেকে গ্রামে, শিক্ষিত থেকে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ কেউই তাকে রাজনীতিতে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিষয়টি ড. ইউনুস খুব দ্রুতই অনুধাবন করতে পারলেন এবং রাজনীতিতে আসার চিন্তা থেকে সরে দাঁড়ালেন। দ্রুতই তিনি তার ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে মননিবেশ করলেন।
অন্তরীন অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার নাম করে হাসিনাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল সরকার। অটল মানষিকতার খালেদা কিছুতেই দেশের বাইরে যেতে রাজি হলেন না। দেশেই চিকিৎসা নিলেন। দুই বড় রাজনৈতিক দলের প্রধান ও অন্য নেতাদের ধীরে ধীরে মুক্তির ফলে দেশের রাজনীতির অঙ্গনের কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্যের আলো দেখা যেতে লাগলো। শীতের কুয়াশার আড়াল ভেঙে সূর্য উঠলে ঘাসের ডগায় শিশির যেমন চিককিক করে ঠিক তেমনি দেশের বাতাসেও রাজনীতির গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো। ধীরে ধীরে মানুষ সোচ্চার হতে লাগলো আর সরকারের অস্বস্তি স্পষ্ট হতে থাকলো।
শেষ কুটচাল দিতে ভুল করেনি ফকরুদ্দিন সরকার। শেখ হাসিনার পাসপোর্টকে কোন গ্রহণ যোগ্য কারণ ছাড়াই জব্দ করা হয়। যার ফলে দেশে ফিরতে ব্রিটিশ বিমান তাকে বহন করতে অস্বীকৃতি জানায়। দেশ ও আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর। অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গিন হতে থাকে। আড়ালে আবড়ালে দেন দরবার চলতে থাকে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা খোঁজতে থাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও সেনা প্রধান। জেনারেল মঈন উদ্দিন আহমেদ এরই মধ্যে ভারতে সফর করে। সেখানেই মূলত নিরাপদ প্রস্থানের নিশ্চয়তা নিয়ে আসে।
জেল থেকে বেরিয়ে এসে খালেদা দৃঢ় কন্ঠে ঘোষণা দিলেন, ক্ষমতায় গেলে অবৈধ ভাবে সরকারে টিকে থাকা, অবৈধ ভাবে আইন প্রণয়ন করা এবং আইনের অপব্যবহারে জন্য বর্তমান সরকার ও তাদের উপদেষ্টাদের বিচারের মুখোমুখি করবেন। তবে রহস্যজনক ভাবে হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব কর্মকান্ডকে দায়মুক্তি দেবার ঘোষণা দিলেন। দেশবাসী যারা রাজনীতির খুঁটিনাটি খোঁজ রাখেন তাদের অনেকই বিস্মিত হলেন। সেনাসমর্থিত যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাইনাস টু ফর্মুলা নিয়ে কাজ করলো,রাজনৈতিক নেতাদের হয়রানি-জেল জুলুম করলো, তাদেরকেই এতো সহজে দায়মুক্তি! হয়তো নিজেদের প্রবোধও দিয়েছেন এই ভেবে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আওয়ামীলীগ একটি নির্বাচনমুখী দল। স্মৃতি হাতড়ে অনেকেই মনে করতে পারলেন সত্তরের নির্বাচনে মৌলানা ভাসানিসহ অনেকেই অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু আওয়ামীলীগ করেছিল। স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাঝ পথে আওয়ামীলীগ আন্দোলন থেকে সরে এসে এরশাদের আহ্বানে তার অধীনে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। তেমনি আজও তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিবে এটা অনুমেয়ই ছিল। করাণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য, মুক্তির পথ, ক্ষমতারও পথ, পালাবলদেরও পথ।
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে খালেদা ও হাসিনার দল। জেলে অন্তরীন হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রেসক্রিপশন মেনে যারা সংস্কারপন্থির খাতায় নাম লিখিয়েছিল তারা ত্রস্ত হয়ে উঠল। খালেদা জিয়া নির্বাচনী প্রস্তুতির শুরুতেই সংস্কারপন্থীদের উপর চড়াও হলেন। সংস্কারপন্থীরা দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন-যারা থেকে গেলেন, দলের সর্বস্তরের তাদের অবস্থান দূর্বল হয়ে পড়লো। তবে শেখ হাসিনা একটু কৌশলের আশ্রয় নিলেন। দলে সংস্কারপন্থীদের সাথে সাথেই বহিষ্কার না করে নির্বাচনের টিকেট দিলেন। নির্বাচনে হাসিনা স্বৈরশাসক এরশাদকে সাথে নিয়ে ভূমিধ্বস জয় পেলেন। যুদ্ধাপরাধী নিজামীর দলকে সাথে নিয়ে খালেদা পরাজিত হলেন।
হাসিনার কৌশলী অবস্থান স্পষ্ট হল সরকার ও মন্ত্রীসভা গঠনের সময়। কোনঠাসা করে রাখলেন সংস্কারপন্থীদের। সংস্কারপন্থী ঝানু নেতাদের মন্ত্রিত্ব না দিয়ে অপেক্ষাকৃত নতুন আর তরুণদের নিয়ে মন্ত্রিসভা ঘোষণা করলেন।
নির্বাচনি ইসতেহারে দেওয়া অন্যতম প্রতশ্রুতি ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার করা। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রথম অধিবেশনেই ঐক্যমত্যে আসে সংসদ। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারকার্যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। প্রচলিত আইনেই প্রসিকিউটর ও আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর ২০১০ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার ও তদন্ত শুরু হয়। নিজামী, কাদের মোল্লা, সাকা চৌধুরী, আব্দুল আলীম, মীর কাসেম, কামারুজ্জামান, মুজাহিদসহ অনেকই গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়।
যাদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে স্বাধীনতার এতোদিন পর বিচার সম্ভব নয় তাদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা ফিরে এলো। সব চেয়ে বেশি হতভম্ব হয়ে গেল জামায়াত। বিএনপিও ধাক্কা খেলো। মুক্তিযুদ্ধা বীর উত্তম জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত দল হলেও, বিএনপি ভেবাচেকায় পড়ে গেল। সাকা চৌধুরী, আব্দুল আলীমদের মতো অনেকেই বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল। সাকা চৌধুরীতো বিএনপির চট্টগ্রামের রাজনীতির বড় একটা স্তম্ভ ছিল। মানবতা বিরোধী অপরধের বিচারে নিজেদের অবস্থান তাই পরিষ্কার করার পরিবর্তে নানা রকম কথার চালে পরিস্থিতি ঘোলা করতে থাকলো। দেশবাসী বিএনপির এই অবস্থান মোটেও ভালো ভাবে গ্রহণ করলো না। রাজনৈতিক জোট ও ভোট সঙ্গী জামায়াতের সাথেই যে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারে বিএনপির অবস্থান-সেই ধারণাই জনমনে বদ্ধমূল হলো।
জামায়াত বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের চেষ্টা করলেও আদালতের অনুমোদন পেল না। ট্রাইব্যুনাল গ্রঠন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেও বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করা গেলো না। দেশ স্পষ্টতই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। একদল বিচারের পক্ষে মতামত দিচ্ছে-আরেক দল গ্রেফতারকৃতদের নির্দোষ ভাবছে। আবার যারা নির্দোশ কিংবা দোষী ভাবছে না তারা বিচার প্রক্রিয়া ও স্বাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ম বহির্ভূত বলে ব্যাখ্যা দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের সম্মুখীন করছে। কেউ কেউ বলতে চাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দেওয়ার পর যে সংক্ষিপ্ত তালিকা ছিলো সেখানে গ্রেফতারকৃত অনেকের নাম ছিলো না। শুধু রাজনৈতিক ভাবে জামায়াতকে কোণঠাসা করতেই এই বিচার শুরু হয়েছে। আওয়ামীলীগে ভেতরে কে কে রাজাকার ছিলো এতোদিনে তারও একটা তালিকা বের করা হয়ে গেল। ফেসবুকে সেই তালিকা ঘুরছে।

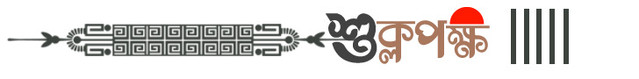








0 Comments